প্রচ্ছদ নিবন্ধ
পড়াশোনা করে যে...
সুস্মিতা কুণ্ডু
"...গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে। তাই তো? জানি জানি।
কিন্তু কেন? যদি না পড়ি? যদি সারাদিন খেলে বেড়াই? যদি ঘুড়ি ওড়াই? যদি টি. ভি. তে ছোটা ভীম, টম অ্যান্ড জেরি দেখি? আচ্ছা যদি গল্পের বই পড়ি? সেটাও তো পড়া, তাই না?"
আচ্ছা, যদি একটা ছোট্ট অবোধ শিশু এই প্রশ্নগুলো করে, কী উত্তর দেব আমরা, কখনও ভেবে দেখেছেন?
হয়ত আমরা বলব যে,
-"ভালো করে পড়াশোনা করলে তবেই তো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, প্রফেসর, এ'সব হ'তে পারবে বড় হয়ে। বাবা মায়ের মুখ উজ্জ্বল করবে, নাম, যশ, অর্থ, সব পাবে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ'বে।"
অবশ্যই, একদম খাঁটি কথা। এভাবেই তো পথ দেখাব কচিকাঁচাগুলোকে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুনে দেব ওদের মনে।
কিন্তু তার আগে একটু সাবধান, একটু সতর্ক হওয়ারও প্রয়োজন আছে।
-----
কেন বলছি এ'কথা?
কারণ, সময়টা বড় কঠিন। এ এমন এক সময় যখন শৈশব বন্দী ঘরের চার দেওয়ালের ভেতরে। শিশু ছড়া শেখে, দাদু দিদার মুখে নয় ইউটিউব থেকে। গেম খেলে এক্স-বক্সে, খোলা নীল আকাশের নিচে সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠে নয়। ঠাকুমার ঝুলি পড়ার বদলে তারা ব্যস্ত কম্পিউটার সার্ফ করতে। এই কম্পিউটার গেমিং-এর নেশা এমনভাবে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধছে, আকর্ষণ করছে কিশোর মনগুলোকে, যে কখনো কখনো তা প্রাণঘাতীও হয়ে উঠছে।
তাই বলছি, সন্তানের মা-বাবাদের এবার নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। আসুন, আমরা গোড়া থেকেই একটু আলোচনা করে দেখি।
------
আধো আধো বুলি ফোটার পর থেকেই একটি শিশুকে ঘন্টার পর ঘন্টা মা বাবার সঙ্গ-ছাড়া হয়ে, যেতে হচ্ছে স্কুলে। ব্যাপারটা মোটেও সহজ নয় একটা শিশুর কাছে । কিন্তু বর্তমান যুগে এটা অবশ্যম্ভাবী। যেখানে নামী স্কুলে ভর্তি করতে গেলে ছ'মাস আগে থেকে ফর্ম তুলতে হয়, মোটা অঙ্কের টাকা জমা করতে হয়, লটারির মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ করতে হয়, মা-বাবা-সন্তান, গোটা পরিবারকে ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে পরীক্ষায় বসতে হয়, সেখানে কোনও মা-বাবাকে এই পরামর্শ দিতে পারি না, যে সন্তানকে আরও একটু দেরিতে স্কুলে ভর্তি করুন। এটা হয়ত আজকের দিনে 'নেসেসারি ইভিল।'
কিন্তু নামী-দামী স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য যেভাবে শিশুটির ওপর মানসিক টর্চার শুরু করে দিই আমরা, ততটা 'ইভিল' হওয়া কি 'নেসেসারি'? অনর্থক তাকে জটিল-কঠিন সব প্রশ্নোত্তর মকশো করাই। সান ইজ 'গোল্ডেন ইয়েলো'-র বদলে যদি শুধু 'ইয়েলো' বলে ফেলে তাহলে দু/তিন বছরের শিশুটির সাথে জেলের কয়েদীর মত ব্যবহার করি। এতটা কঠোর হওয়ার কি প্রয়োজন আছে? একটু কম নামী স্কুলেই না হয় ভর্তি হ'ল। মনে করে দেখুন তো, আমাদের সবার ছোটোবেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো কি হার্ভার্ডের মিনি সংস্করন ছিল? আপনারা "রামধনু" সিনেমাটি দেখেছেন? না দেখে থাকলে অনুরোধ করব দেখতে। না সিনেমার মতো বাস্তবে সব কিছু ঘটে না বা সেরকমটা অনুসরণ করাও সম্ভব নয়। তবু কিছুটা হ'লেও চোখের সামনে নিজেদের প্রতিচ্ছবিটা ভেসে ওঠে।
--------
বড় জায়গায় ভর্তি হলেই, পাঁচনের মতো সব বিদ্যে তাকে তো কেউ গুলে খাইয়ে দেবে না, তাইনা? বরং কিছুটা দায় নিজের ঘাড়ে তুলে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। গৃহশিক্ষক বা স্কুলের ভরসায় সব ছেড়ে না দিয়ে নিজেও একটা খুঁট ধরে রাখুন। অনেকে হয়ত বলবেন, অনেক মা বাবার নিজেদের পড়ানোর যোগ্যতা বা সময় নেই বলেই তো সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ার দায়িত্ব অন্যের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হ'ন। সেই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ল বলি। আমার দিদিমার মাত্র বারো বছর বয়সে ক্লাস ফাইভ/সিক্সে পড়াকালীন আমার দাদুর সাথে বিয়ে হয়। তারপর আর পড়াশোনার সুযোগ হয়নি। মা, মাসিদের মুখে শুনি, সেই দিদিমাই কিন্তু অনেক উঁচু ক্লাস অব্দি মায়েদের নিজেই পড়াত, কোনো গৃহশিক্ষক ছিল না মায়েদের। দিদা নিজে পড়ে পড়ে শিখে শিখে মায়েদের পড়াত। ঠাকুমা আদ্যান্ত গ্রামের মানুষ, তাঁর স্টোরিটাও একরকমই। সে আমলের মানুষেরা যদি পারেন, আমরা পারিনা একটু চেষ্টা করতে?
এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অধিকাংশ মানুষেরই এখন সময়ের বড্ড অভাব। আচ্ছা, একটু চেষ্টা করলে, সারাদিনের শেষে বা সপ্তাহান্তে কিছুটা সময় বার করা যায় না নিজের সন্তানের জন্য? কড়ায় সব মশলা আনাজ তেল জল চাপিয়ে আগুনে বসিয়ে দিলেই কি সুস্বাদু ব্যঞ্জন তৈরী হয়ে যায়, বলুন তো? তাকেও সময়ে সময়ে নাড়তে চাড়তে হয়। তেমনি বাচ্চাকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেই বা একগণ্ডা গৃহশিক্ষক নিয়োগ করে দিলেই আমাদের সব দায়িত্ব তো শেষ হয়ে যায় না।
ধরুন সারাদিনের কাজের শেষে বাড়ি ফিরেছেন, একটু টি. ভি. তে খবর শুনবেন, একটু সিরিয়াল দেখবেন, গান শুনবেন, রান্না বসাবেন। পাশের ঘরে তাকে পড়তে পাঠিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবেন না, বা তাকে হাতের স্মার্টফোনটা ধরিয়ে দিয়ে নিজের কাজে মেতে যাবেন না। এই সবের ফাঁকেই যদি বাচ্চাকেও দলে টেনে নেওয়া যায়, কেমন হয়? বিজ্ঞাপনের বিরতিতে ওকে দু'টো করে অঙ্ক কষতে দিন, একটু পড়া ধরুন, খুব ছোট্ট বাচ্চা হ'লে আম, কাঁঠাল, মাছ, ফুল, পাখি, স্কেচ করে দিয়ে তাতে ক্রেয়ন ঘষতে বলুন। ল্যাপটপে বসে অফিসের কাজ করার সময়, ওকেও পাশে বসিয়ে হিজিবিজি যা মন চায় লিখতে উৎসাহ দিলে, বাচ্চাটির মধ্যেও একটা সু-অভ্যাস গড়ে উঠবে।
রাত্রে ঘুমোনোর আগে একটা ছোট্ট রিচ্যুয়াল তৈরী করা যায়। আপনার সারাদিনের খবর সহজ ভাষায় ওকে দিন আর ওর স্কুলের গল্পগুলোও মন দিয়ে জেনে নিন এই সুযোগে। ওর কোন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ, কী ধরনের এক্সট্রাকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিতে ও সবচেয় বেশি আনন্দ পায়, খোঁজ নিন। নাচ, গান, আঁকা যেটা ভালোবাসে সেটা ওকে শেখানোর চেষ্টা করুন।
ব্যক্তিগতভাবে বলব, শুরুতেই বড় বড় প্রতিষ্ঠানে বাচ্চাকে ভর্তি করে দিয়ে যদি প্রত্যাশা করতে থাকি যে সে খুব বড় আর্টিষ্ট হয়ে উঠবে, বা টি. ভি.-তে রিয়েলিটি শো-তে চান্স পেয়ে সবার সামনে আমাদের গর্বিত করবে, সেটা ভারী অবিচার করা হবে শিশুগুলোর ওপর। বাবা মা নিজেরা যেগুলো পারেন, সেগুলো অল্প অল্প করে নিজেরাই বাড়িতে তালিম দেওয়া বরং অনেক বেশি ভালো।
নাহলে কখন যে ধীরে ধীরে ওর ভালো-লাগার, শখের জিনিসটা ওর কাছে বোঝা হয়ে উঠবে, সেটা আমরা টেরও পা'বনা।
--------
এ তো গেল একদম ছোট্টবেলার কথা। এরপর ধীরে ধীরে যত বড় হবে তত সমস্ত কিছু কঠিন হ'তে থাকবে, শিশু এবং অভিভাবক দু'পক্ষের জন্যই। স্কুলব্যাগের ওজন ক্রমবর্ধমান হবে, বইগুলো দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বাড়তে থাকবে, পরীক্ষার সংখ্যা বাড়বে, সেই সাথে পাশ-ফেল-ফার্স্ট-সেকেণ্ড এসবের হিসেব শুরু হবে। সমস্যার তালিকাটাও তাল মিলিয়ে লম্বা হতে থাকবে।
একদিনের ঘটনা বলি, বাসে করে ফিরছি, পাশের সিটে একজন মা তাঁর বছর বারো তেরোর ছেলেকে নিয়ে ফিরছেন। বোঝাই যাচ্ছে স্কুলের পরীক্ষা চলছে, হাতে প্রশ্নপত্র ধরা মায়ের। কামান দাগার মত প্রশ্ন করে চলেছেন ছেলেকে, উত্তর মেলাচ্ছেন, ভুল বেরোলেই বাসভর্তি লোকের সামনে যাচ্ছেতাই করে বকে চলেছেন। বকুনির সারমর্ম এটাই যে,
"এত খরচ করে ভালো স্কুলে ভর্তি করানো হ'ল, এত প্রাইভেট টিউশন দেওয়া হ'ল। নিজেদের টি. ভি দেখা, সিনেমা দেখা সব জলাঞ্জলি দিয়ে ওর পেছনে সময় দেওয়া হ'ল, আর তার প্রতিদান, এই !!"
বাজি রেখে বলতে পারি, এই দৃশ্যর সাথে একাধিকবার আমাদের সকলেরই কমবেশি পরিচয় হয়েছে। কখনও সামনে ঘটতে দেখেছি, কখনও বা নিজেরা ভিকটিম হয়েছি, কখনও বা আমরাই ওই মা-এর চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছি। আপাতদৃষ্টিতে খুব সাধারণ ঘটনা দেখতে লাগলেও, এই পুরো ব্যাপারটাই অত্যন্ত আপত্তিজনক, বিভিন্ন কারণে।
প্রথমতঃ, একটি শিশু, যার মনে ধীরে ধীরে আত্ম-সচেতনতা গড়ে উঠছে, মান-সম্মান বোধ জাগছে, তাকে এভাবে চেনা-অচেনা লোকের সামনে অপমান করলে, তার মনোবল তলানিতে ঠেকবে। হয় সে প্রচণ্ড গুটিয়ে নেবে নিজেকে নতুবা অ্যাগ্রেসিভ হয়ে উঠবে। দুটোই ওর ভবিষ্যতের উন্নতির পথে বড় অন্তরায়।
দ্বিতীয়তঃ, এভাবে পরীক্ষার মাঝপথে, যে বিষয়টা হয়ে গেল, তার ভুলভ্রান্তিটা নিয়ে আলোচনা করতে বসলে, পরের দিনের পরীক্ষাটায় তার প্রভাব মোটেই সন্তোষজনক হবে না। বলছি না যে সন্তানের পরীক্ষা কেমন হ'ল তাই নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়াটা কোনও অপরাধ। কিন্তু ক'টা দিন অপেক্ষা করে, একদম পরীক্ষার শেষে প্রশ্নপত্র নিয়ে আলোচনায় বসাটাই মনে হয় শ্রেয়।
তৃতীয় এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি, সেটি হ'ল, পুরো ঘটনাটায় অভিভাবকের মানসিকতার প্রতিফলনটি। সন্তানকে পৃথিবীতে তো আমরাই আনি। সে বেচারা ছোট্ট মানুষটি তো আর নিজে থেকে আসেনি। কাজেই তার জন্য যতটা আমরা, মা বাবারা করছি বা করব, সেটার পেছনে কেন জটিল অঙ্কের, দেনা পাওনার হিসেব কষব বলুন তো! গয়না বেচে তাকে পড়ালাম বা চাকরি ছেড়ে তার পেছনে সময় দিলাম, সেটার প্রতিদান আশা করার নামে তার ওপর ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়াটা অপরাধ।
-------
এইরকম এক বিভীষিকার মধ্যে দিয়ে পরীক্ষা তো উতরোয়, তারপর আসে ফল প্রকাশের দিনটি। নাহ্! সন্তুষ্ট আজকাল আমরা মনে হয ১০০ তে ১০০ পেলেও হ'ইনা। আরেকটা ছোটো ঘটনা বলি। প্রাইমারি স্কুলে পড়ি, কোনো পরীক্ষাতেই প্রথম আর হ'ইনা। বাবা-মা দুঃখ করে প্রকাশ করে তাতে খানিকটা। তাঁদের খুব সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলাম, "আমি ফার্স্ট হলে, অমুক কী হবে? তমুক কী হবে? ওরা কষ্ট পাবেনা বলো?"
সত্যিই তো, প্রথম তো একজনই হয়। বাকি সবাই কি তাহলে প্রথম না হতে পারার জন্য তিরস্কৃত হবে? অনেক সময়ই প্রথম না হতে পারা শিশুটিকে, আমরা অভিভাবকরা অন্য কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সাথে তুলনা করতে থাকি। আত্মীয় স্বজনের মেধাবী পুত্র কন্যার উদাহরণ দিয়ে দিয়ে তার সেল্ফ-এস্টিমের দেওয়ালে বোমা-বর্ষণ করি। কত অবিশ্বাসের ছিদ্র যে সেই কনফিডেন্স-এর পাঁচিলে হয়, কত ভরসার ইঁট যে খসে পড়ে, আমরা বুঝিনা। ভয়ংকর ক্ষতি হয়ে যায় আমাদের সকলের অগোচরে। প্রসঙ্গত আরেকটি সিনেমার কথা বলব, "ইচ্ছে"।
যদি না দেখা থাকে, একবার দেখতে পারেন।
-----
এই সব পরীক্ষার গণ্ডি টপকে অবশেষে আসে 'বড় পরীক্ষা'। দশম শ্রেণীর, বোর্ড-এর পরীক্ষা। জীবনের প্রথম স্কুলের বাইরের বড় পরীক্ষা। এই পরীক্ষার ফলাফলই নাকি স্থির করে দেবে একজন কিশোর বা কিশোরীর জীবন কোন খাতে বইবে এবার। অসম্ভব একটা মানসিক চাপ সৃষ্টি হয় সদ্য কৈশোরে পা দেওয়া ছেলেমেয়েগুলোর ওপর। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই পরীক্ষার সার্টিফিকেট-টি বয়সের প্রমাণপত্র হয়ে থেকে যায়। কারণ, বহু ভাল ফল করা ছাত্র-ছাত্রী, আবার দু'বছর পরের বোর্ড পরীক্ষাতেই আশানুরূপ ফল করতে পারে না। আবার অনেকেই এই পরীক্ষায় ভাল ফল না করলেও পরের পরীক্ষায় চমকপ্রদ রেজাল্ট করে। তবে কি জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষার কোনও গুরুত্ব নেই? অবশ্যই আছে, তথাকথিত সাফল্য এবং ব্যর্থতা দুটোরই নিরিখে। 'সাফল্য' আগামী পথটা কিছুটা সুগম করে দেয়। আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, পছন্দের বিষয় নির্বাচন, পছন্দের স্কুল কলেজে ভর্তি, এগুলো সহজসাধ্য হয়। তেমনই আবার 'ব্যর্থতা' কোথাও যেন একটা ঈঙ্গিত দেয় যে, ভবিষ্যতের পথটা মসৃণ নয়। অতএব এখন থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে, কোমর বেঁধে লাগতে হবে।
কোন বিষয় নিয়ে সন্তান পড়াশোনা করবে সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা অভিভাবকরা নির্ধারণ করার চেষ্টা করি। তার প্রাপ্ত নম্বরের ওপর ভিত্তি করে, ভবিষ্যতে চাকরির সহজলভ্যতা, নিরাপত্তা, সুযোগ-সুবিধে, নাম-যশ, ইত্যাদি গুণাগুণ বিচার করে আমরা তাকে ঠেলে দিই আমাদের পছন্দের অভিমুখে। কিন্তু আমাদের কাছে যেটা উত্তরণের সিঁড়ি সেটা তার কাছে খাদের কিনারাও হতে পারে। এভাবে পাপেটের মত সন্তানকে পরিচালনা না করে তাকে একটু ফ্রিডম দেওয়াটা বেশি জরুরী। পছন্দের বিষয় ও নিজেই বাছুক না। কোনো বিষয়ে বেশি নম্বরটাই মাপকাঠি নয়। ভালোলাগার বিষয় নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগোলে অনেক ভালো ফল করবে নিশ্চয়ই।
তবে হ্যাঁ, যেহেতু ওদের বাইরের জগত সম্পর্কে ধারনাটা স্বচ্ছ নয়, চিন্তাভাবনাও খুব বেশি পরিণত নয়, তাই সবসময় ওদের পাশে পাশে থাকতে হবে। ওদের গাইড করতে হবে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে প্রফেশনাল কেরিয়ার কাউন্সেলিং সেন্টারগুলোর সাহায্য নিতে হবে। নিজেদের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী সন্তানকে এগোতে দেওয়াটা বাস্তবসম্মত। তাছাড়া আজকাল 'এডুকেশনাল লোন' বস্তুটি আর ভিন-গ্রহের ব্যাপার নয়, পদ্ধতিটাও রকেট সায়েন্সের মত কঠিন নয়।
-----
এর পর আসি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে। শুরুতেই বলছিলাম, সত্যিই কি পড়াশোনা করলে তবেই একমাত্র গাড়ি চাপা যায়, অর্থাৎ কিনা 'সফল' হওয়া যায় জীবনে? এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে মান্ধাতার আমলের এই ধ্যান-ধারনা আর প্রযোজ্য নয় মোটেই। আমাদের চারপাশে তাকালেই ক'ত কৃতী মানুষের উদাহরণ রয়েছে, যাঁরা লেখাপড়া ছাড়াও অন্য প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে অনেক উঁচুতে উঠেছেন, সাফল্যমণ্ডিত হয়েছেন।
তাই, স্কুলের গণ্ডী টপকানোর পর প্রথাগত শিক্ষার পথে না গিয়ে কেউ যদি অন্যপথে যায় তাতে, 'গেল গেল রব' তোলার কিছু নেই। কারোর অনুকরণ করে বা অনুসরণ করে খুব বেশি দূর যাওয়া যায়না। নিজের পথ নিজে গড়ে নিতে পারে যে জন, তাকে আটকায় কার সাধ্য। মন প্রাণ ঢেলে যে জিনিসের সাধনা করা হয়, তাতে দেরিতে হলেও সাফল্য আসবেই। এইটুকুন ভরসা তো আমরা আমাদের সন্তানদের ওপর রাখতে পারি, তাই না?
শুধু কেরিয়ার এর দিক দিয়েই নয়, মানুষ হিসেবেও ওরা যাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, সেই শিক্ষাটা দেওয়া সবচেয়ে বেশি জরুরী।
------
সন্তান জন্মানোর সাথে সাথে মা-বাবারও জন্ম হয়। ওরা যেমন হাঁটতে কথা বলতে শেখে, আমরাও শিখি ওদের সঠিক পথটা দেখিয়ে দিতে, ভালো মন্দের তফাৎ বোঝাতে। আসলে কী বলুন তো, এটা একটা দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটার ব্যালেন্সের খেলার মতো। অতিরিক্ত শাসন, বাড়াবাড়ি রকমের কন্ট্রোল, এগুলো যেমন করাটা উচিত নয়, তেমনি অবাধ স্বাধীনতা, ফুল ডিসিশন মেকিং পাওয়ার, এটাও ওদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। কোনও একদিকের ভার বেশি হলেই দড়ি থেকে পতন অনিবার্য।
পরিশেষে আরেকটা কথা বলি। সন্তান মানুষ হোক, স্বাবলম্বী হোক, তার সাথে সাথে আমাদেরও স্বাবলম্বী হয়ে ওঠাটা জরুরী। ওদের মানুষ করেছি বলেই বাকি জীবনটা মা-বাবা ওদের লায়াবিলিটি যেন না হয়। সন্তানের কাছে থাকা আর বৃদ্ধাশ্রমে থাকা, এই দুই এর মাঝে আরেকটা অবস্থান আছে। নিজের কাছে, নিজের মতো করে, ভালো থাকা। ওরা একটু একটু করে লক্ষ্যের দিকে এগোনোর সাথে সাথে, আমাদের, মা-বাবাদেরকেও একটু একটু করে খাঁচার দরজাটা খুলে দিতে হবে। ডানা মেলুক না ওরা মুক্ত আকাশে। আর আসুন না আমরাও শক্ত মাটিতে পা রেখে ওদের সেই উড়ান দেখি। আনন্দাশ্রুটা মুছে দু'চোখ ভরে দেখি, পরিযায়ী পাখীর আসা-যাওয়া।
















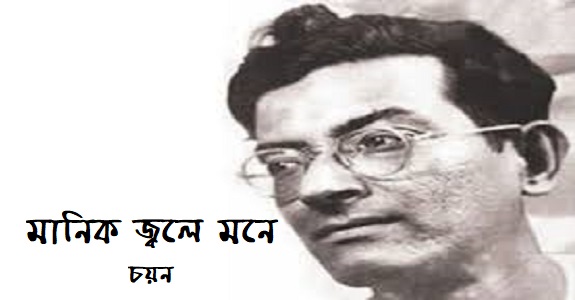














0 comments: