৮
শিবপালগঞ্জ গাঁ বটে, কিন্তু বসেছে শহরের কাছালাছি বড় রাস্তার ধারে। অতএব বড় বড় নেতা ও অফিসারকুলের এখানে আসতে কোন নীতিগত আপত্তি হওয়ার কথা নয়। এখানে শুধু কুয়ো নয়, টিউবওয়েলও আছে। বাইরে থেকে দেখতে আসা বড় মানুষেরা তেষ্টা পেলে প্রাণসংশয় না করেই এখানকার জল খেতে পারেন। এইসব ছোটখাট অফিসারের মধ্যে কোন না কোন এমন একজন দেখা দেন যে তাঁর ঠাটবাট দেখে স্থানীয় লোকজন বুঝে যায় যে এ এক্কেবারে পয়লা নম্বরের বেইমান। অথচ ওকে দেখে বাইরের লোকজন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে—কী ভদ্র, কী ভালো!নিশ্চয় কোন বড় ঘরের থেকে এয়েচে।দেখ না, আমাদের চিকো সায়েব এর সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। ফলে খিদে পেলে এঁরা নিজেদের চরিত্রে কোন দাগ না লাগিয়েও বিনা দ্বিধায় এখানে খেয়ে নিতে পারেন। কারণ যাই হোক, সেবার শিবপালগঞ্জে জননায়ক আর জনসেবক—সবার আনাগোনা বড্ড বেড়ে গেছল। শিবপালগঞ্জের বিকাস ও উন্নয়ন নিয়ে সবার বড্ড চিন্তা। তাই তারা যখন তখন লেকচার দিতে থাকেন।
এই লেকচারপর্বটি গঞ্জহাদের জন্যে ভারি মজার। কারণ এতে গোড়ার থেকেই বক্তা শ্রোতাকে এবং শ্রোতা বক্তাকে হদ্দ বোকা ধরে নেয়। আর এটাই সব গঞ্জহা্দের জন্যে আদর্শ পরিস্থিতি বটে! তবু, লেকচার এত বেশি হলে শ্রোতাদের পক্ষে হজম করা কঠিন হয়ে পড়ে! লেকচারের আসল মজা হল—যখন শ্রোতা বুঝে যায় লোকটা ফালতু বকছে আর বক্তা নিজেও বোঝে যে ও ফালতু বকবক করছে। কিন্তু কিছু লোক এমন গম্ভীর মুখে লেকচার দেয় যে শ্রোতারা সন্দেহ করতে বাধ্য হয় যে লোকটা যা বকছে সেটা নিজে অন্ততঃ বিশ্বাস করে। এ’জাতীয় সন্দেহ হলেই লেকচারটা বেশ গাঢ় এবং পানসে হয়ে যায় এবং শ্রোতাদের পাচনশক্তির ওপর চাপ হয়ে যায়। এইসব দেখেশুনে গঞ্জহার দল যে যার হজম করার ক্ষমতা মেপে ঠিক করে নেয়—কে কখন লেকচার শুনবে। কেউ খাবার খাওয়ার আগে তো কেউ দুপুরের ভোজনের পর। তবে বেশিরভাগ লোক লেকচয়ার শুনতে আসত দিনের তৃতীয় প্রহরের ঝিমুনি থেকে সন্ধ্যাবেলায় জেগে ওঠার মাঝের সময়টুকুতে।
সেসব দিনে গাঁয়ে গাঁয়ে লেকচার দেবার মুখ্য বিষয় ছিল ‘ কৃষি’। তার মানে আগে লেকচারের জন্যে অন্য কোন বিষয় ছিল এমনটা ভাববেন না যেন!আসলে গত কয়েকবছর ধরে কৃষকদের পটিয়ে পাটিয়ে বোঝান হচ্ছে যে আমাদের এই ভারতবর্ষ কিন্তু একটা কৃষিপ্রধান দেশ। গেঁয়ো শ্রোতারা কক্ষণো এ’নিয়ে আপত্তি করেনি।তবে প্রত্যেক বক্তা লেকচারব শুরু করার আগে ধরে নিতেন যে শ্রোতারা নিশ্চয়ই আপত্তি করবে। তাই ওঁরা খুঁজেটুজে একের পর এক নতুন যুক্তি সাজাতেন আর কোমর কষে প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন যে ভারত অবশ্য একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এরপর ওঁরা বলতে শুরু করতেন—চাষবাসের উন্নতি মানেই দেশের উন্নতি।তবে এর পরে আরও কিছু বলার আগেই দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে যেত। তখন ওই শান্ত সুভদ্র অফিসারটি, মানে যে খুব বড়ঘরের ছেলে এবং যার সঙ্গে চিকো সায়েব নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, বক্তার পিঠের কাপড়ে টান মেরে মেরে ইশারায় বলার চেষ্টা করত, চাচাজি, রান্না হয়ে গেছে। কখনও কখনও এমন হতে যে বাকি বক্তারা এর পরের কথাগুলোও বলে ফেলতেন, তখন স্পষ্ট হত যে এনাদের আগের আর পরের বক্তব্যে বিশেষ ফারাক নেই।
ঘুরেফিরে একটাই কথাঃ ভারত একটি কৃষিপ্রধান দেশ আর তোমরা হলে কৃষক। ভাল করে চাষ কর বাছারা, বেশি বেশি ফসল ফলাও। সব বক্তার মনেই একটা সন্দেহের ঘুর্ঘুরে পোকা কুরকুর করত- চাষারা বোধহয় বেশি ফসল ফলাতে চায় না।
লেকচারে যা খামতি থাকত তা’ বিজ্ঞাপনে পুষিয়ে যেত। একদিক দিয়ে দেখলে শিবপালগঞ্জের দেয়ালে লেখা বা সাঁটা বিজ্ঞাপন জনপদটির সমস্যা ও তার সমাধানের সঠিক পরিচয়। উদাহরণ দিচ্ছি, সমস্যাটা হল ভারত এক কৃষিপ্রধান দেশ এবং বদমাশ চাষাগুলো বেশি করে ফসল ফলাতে উৎসাহী নয়। এর সমাধান হল চাষিদের খুব লেকচার দেয়া হোক এবং ভাল ভাল ছবি দেখানো হোক। তাতে মেসেজ দেয়া হবে যে তুমি নিজের জন্যে না হোক, দেশের জন্যে তো ফসল ফলাও!এভাবেই কৃষকদের ‘দেশের জন্যে ফসল উৎপাদন করো’ গোছের পোস্টার দেয়ালে দেয়ালে ভরে গেল। চাষিদের উপর পোস্টার আর ছবির মিশ্রিত প্রভাব এমন হল যে সবচেয়ে সাদাসিদে চাষিও ভাবতে লাগল যে এর পেছনে সরকারের নিশ্চয়ই কোন চাল আছে।
একটা বিজ্ঞাপন তখন শিবপালগঞ্জে সাড়া ফেলে দিয়েছিল যাতে মাথায় কষে বাঁধা গামছা, কানে কুন্ডল, গায়ে মেরজাই একজন হৃষ্টপুষ্ট চাষি বুকসমান উঁচু গমের শীষ কাস্তে দিয়ে কাটছে। ওর পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন বঊ যার ঠোঁটে কৃষিবিভাগের অফিসারমার্কা হাসি; একেবারে আপনহারা-মাতোয়ারা ভাব। বিজ্ঞাপনের নীচে এবং উপরে ইংরেজি ও হিন্দিতে লেখা-“ অধিক ফসল ফলাও”। মেরজাই পরা কাস্তে হাতে চাষীদের মধ্যে যে ইংরেজি অক্ষর চেনে তাকে ইংরেজিতে এবং যে হিন্দি চেনে তাকে হিন্দিতে পটকে দেওয়ার উদ্দেশে এই বিজ্ঞাপনটি তৈরি। আর যারা ইংরেজি বা হিন্দি কিছুই চেনে না তারা অন্ততঃ হাসিমুখ চাষিদম্পতিকে তো চিনবেই। আশা করা যায় চাষির পেছনে হাসিমুখ বৌয়ের ফটোটি দেখা মাত্র ওরা মুখ ঘুরিয়ে পাগলের মত ‘অধিক অন্ন’ ফলাতে লেগে যাবে। কিন্তু বিজ্ঞাপনটির আজকাল মাঠেঘাটে চর্চার কারণ অন্য। বিশেষজ্ঞদের মতে পুরুষটির চেহারা খানিকটা যেন বদ্রী পালোয়ানের সঙ্গে মেলে। কিন্তু মেয়েটি কে এ’নিয়ে রসিকদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ দেখা গেল। এই গাঁয়ের অনেক মেয়েছেলের মধ্যে ভাগ্যবতীটি কে তা’নিয়ে আজও ফয়সালা হয় নি।
তবে সবচেয়ে উচ্চকিত বিজ্ঞাপন চাষের নয় ম্যালেরিয়ার। নানান জায়গায় বাড়ির দেয়ালে পাটকিলে রঙে লেখা হল—‘ম্যালেরিয়া খতম করব ভাই, তোমার সবার সাহায্য চাই‘ এবং ‘মশার বংশ হবে ধ্বংশ’। এই প্রচারের পেছনেও ধারণা ছিল যে কিসান গরু-মোষের মত মশাপালনে আগ্রহী। তাই মশা মারার আগে ওদের হৃদয়-পরিবর্তন করা দরকার। হৃদয়-পরিবর্তন করতে দাপট দেখানো দরকার, আর দাপট দেখাতে ইংরেজি চাই।এই ভারতীয় তর্ক-পদ্ধতি অনুসরণ করে ম্যালেরিয়া-নাশ্ বা মশক-লাশ করার সমস্ত আপিল প্রায় সবটাই ইংরেজিতে লেখা অতএব লোকজন এই বিজ্ঞাপনগুলোকে কবিতা নয়, চিত্রকলা বা আলপনা হিসেবে মেনে নিল। তাই নিজেদের বাড়ির দেয়ালে পাটকিলে রঙের ইচ্ছেমত ইংরেজি লেখার অনুমতি দিয়ে দিল। দেয়ালে দেয়ালে ইংরেজি আলপনা আঁকা চলতে থাকল, মশাও মরতে লাগল, কুকুর ঘেউ ঘেউ করে চলল আর লোকজন নিজের পথে চলতে থাকল।
একটা বিজ্ঞাপন সাদাসিদে ঢঙে বলছে—আমাদের সঞ্চয় করা উচিত। কিন্তু গাঁয়ের মানুষকে ওদের পূর্বপুরুষেরা মরার আগে শিখিয়ে গেছেন—দু’পয়সা বাঁচানোর চেষ্টা করা উচিৎ। আর এই নীতিকথাটি গ্রামের সবার ভালো করে জানা আছে। তবে এরমধ্যে নতুনত্ব এইটুকু যে এখানেও দেশ জুড়ে দেয়া হয়েছে। মানে নিজের জন্যে নাহোক, দেশের জন্যে তো সঞ্চয় কর।
হক কথা। বড় মানুষেরা- যত শেঠ-মহাজন, উকিল, ডাক্তার—সবাই পয়সা বাঁচায় নিজেদের জন্যে। তাহলে দেশের জন্যে সঞ্চয় করতে ছোট ছোট চাষির দল, গরীব-গুর্বোর কোন আপত্তি হওয়ার কথা নয়। সবাই নীতির হিসেবে ঐক্যমত যে পয়সা বাঁচানো উচিৎ। এখন সঞ্চিত অর্থ কোথায় এবং কীভাবে জমা করতে হবে তাও লেকচারে এবং বিজ্ঞাপনে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। তাতেও লোকজনের কোন আপত্তি নেই। শুধু এটাই বলা হয়নি যে সঞ্চয় করারা আগে তুমি যে খাটাখাটনি করবে তার জন্যে তোমার মজুরি কত হওয়া চাই।
পয়সা বাঁচানোর ব্যাপারটা যে আয় ও ব্যয়র সঙ্গে যুক্ত, এই ছোট্ট কথাটা বাদ দিয়ে বাকি সব বিজ্ঞাপনে বলা রয়েছে। মানুষজন ভাবল—বেচারা বিজ্ঞাপন, চুপচাপ দেয়ালে সেঁটে রয়েছে, খেতে চাইছে না, পরতে চাইছে না, কাউকে যেমন কিছু দিচ্ছে না, তেমনই কারও কাছে কোন আবদার করছে না। যেতে দাও, খোঁচাখুঁচি কর না।
কিন্তু রঙ্গনাথকে হাতছানি দিচ্ছে যে বিজ্ঞাপনগুলো তারা আদৌ পাব্লিক সেক্টরের নয়, বরং এই বাজারে প্রাইভেট সেক্টরের অবদান।এদের থেকে উৎসারিত আলোর নমুনা দেখুন। এলাকায় সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়া ব্যামো হল দাদ।বিজ্ঞাপনটি বলছে, “এমন একটা ওষুধ পাওয়া গেছে যেটা দাদের উপর লাগিয়ে দিলে দাদের শেকড় অব্দি উপড়ে আসে, মুখে পুরে ফেললে সর্দি-কাশি সেরে যায়, আর বাতাসায় ভরে জলের সঙ্গে গিলে ফেললে কলেরা সারাতে কাজ দেয়। এমন ওষুধ কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। এর আবিষ্কারক এখনও জীবিত, শুধু বিলেতের সাহেবসুবোর চক্রান্তে উনি আজও নোবেল পাননি’।
এ দেশে এধরনের নোবেল না পাওয়া আরও বড় বড় ডাক্তার রয়েছেন। একজন থাকেন জাহানাবাদ জনপদে। ওখানে ইদানীং বিদ্যুৎ এসে গেছে। তাই উনি নপুংসকতার চিকিৎসা বিজলির শক দিয়ে করছেন। নপুংসকদের কপাল ফিরেছে।আর একজন বিখ্যাত ডাক্তার, অন্ততঃ গোটা ভারতে খুব নামডাক, বিনা অপারেশনে অণ্ডকোষ বৃদ্ধির চিকিৎসা করেন। আলকাতরার পোঁচ দিয়ে লেখা এই জরুরি খবরটি শিবপালগঞ্জের যেকোন দেয়ালে দেখা যেতে পারে। মানছি, অনেকগুলো বিজ্ঞাপন বাচ্চাদের শুকনো কাশি, চোখের অসুখ এবং আমাশা ইত্যাদি নিয়ে। কিন্তু আসল রোগ হল হাতে গোণা তিনটি—দাদ, অন্ডকোষের ফোলা এবং নপুংসকতা। শিবপালগঞ্জের ছেলেপুলের দল অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে এসব রোগের চিকিৎসার বিষয়েও দেয়াললিপির মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করতে থাকে।
বিজ্ঞাপনের এমন ভীড়ের মাঝে বৈদ্যজীর বিজ্ঞাপনটি—”নবযুবকদের জন্যে আশার কিরণ” -আলাদা করে চোখে পড়ে। এটি ‘নপুংসকদের জন্যে বিজলীচিকিৎসা” গোছের অশ্লীল দেয়াললিপিগুলোর সঙ্গে লড়ালড়ি এড়িয়ে যায়। এবং ছোট ছোট গলি চৌমাথা দোকান এবং সরকারি অফিসগুলোর গায়ে—যেখানে ‘প্রস্রাব করিবেন না’ এবং ‘বিজ্ঞাপন মারিবেন না’ বলে সবাই জানে- টিনের ছোট ছোট তক্তির ওপর লালসবুজ অক্ষরে দেখা দেয়। তাতে ‘নবযুবকদের জন্যে আশার কিরণ’, নীচে বৈদ্যজীর নাম এবং দেখা করার সময় – এটুকুই লেখা থাকে।
একদিন রঙ্গনাথের চোখে পড়ল যে রোগের চিকিৎসায় একটা নতুন উপসর্গ এসে জুটেছে ববাসীর(অর্শ)! সাতসকালে কয়েকজন মিলে একটি দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে লিখতে শুরু করেছে—‘ববাসীর’।
এ তো শিবপালগঞ্জের বিকাশ শুরু হওয়া! এই শব্দটির চারটে প্রমাণ সাইজ অক্ষর যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে- এখন আমাশার যুগ চলে গেছে। ধীরে ধীরে হাঁটিহাঁটি, পা-পা করে এন্ট্রি নিচ্ছে নরমসরম শরীর, অফিসের চেয়ার, সভ্যভব্য চালচলন, দিনভর চলতে থাকা খাওয়াদাওয়া এবং হালকা পরিশ্রমের যুগ। আর দিকে দিকে ব্যাপ্ত ‘নপুংসকতা’র মোকাবিলা করতে আধুনিকতার প্রতিনিধি হিসেবে লড়াইয়ের ময়দানে নামছে ‘ববাসীর’। বিকেল নাগাদ ওই দানবীয় আকারের বিজ্ঞাপন একটা দেয়ালে নানারঙে সেজে দিকে দিগন্তে উদঘোষ করতে লাগল—“ ববাসীরের বাজি রেখে চিকিৎসা!
দেখতে দেখতে চার-পাঁচ দিনেই সারা দুনিয়া ববাসীরের বাজি রেখে সারিয়ে তোলার দম্ভের সামনে নতজানু হল।চারদিকে ওই বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। রঙ্গনাথ হতভম্ব, একই বিজ্ঞাপন একটি দৈনিক খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে! কাগজটি রোজ সকাল দশটা নাগাদ শিবপালগঞ্জে পৌঁছিয়ে লোককে জানান দেয় যে স্কুটার ও ট্রাকের সংঘর্ষ কোথায় হয়েছে, আব্বাসী নামক তথাকথিত গুন্ডা ইরশাদ নামের কথিত সব্জিওলাকে তথাকথিত ছুরি দিয়ে কথিত রূপে কোথায় আঘাত করেছে।
সেদিন রঙ্গনাথের চোখে পড়ল যে ওই পত্রিকার প্রথম পাতার একটা বড় অংশ কালো রঙে লেপে দেয়া আর তার থেকে বড় বড় সাদা অক্ষরে ঝলসে উঠছে—ববাসীর! অক্ষরের ছাঁদ একেবারে দেয়াললিপির বিজ্ঞাপনের মত। ওই অক্ষরগুলো ববাসীর(অর্শ)কে এক নতুন চেহারা দিল আর আশপাশের সবকিছু যেন ববাসীরের অধীনস্থ কর্মচারি হয়ে গেল। কালো প্রেক্ষাপটে ঝকঝকে ববাসীর সহজেই লোকের চোখ টানল।এমনকি যে শনিচর বড় বড় অক্ষর পড়তে গেলে হিমসিম খায়, সেও পত্রিকার কাছে সরে এসে অনেকক্ষণ মন দিয়ে চোখ বুলিয়ে রঙ্গনাথকে বলে উঠল—হ্যাঁ, চীজ বটে!
এই কথাটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন গর্ব রয়েছে। মানে শিবপালগঞ্জের দেয়ালে ঝকমক করা বিজ্ঞাপন কোন সাধারণ বস্তু নয়, শহরের কাগজেও ছেপে বেরোয়। এভাবে বোঝা গেল যে যা রয় শিবপালগঞ্জে, তা’ রয় বাইরের কাগজে।
তক্তপোষের উপর বসে ছিল রঙ্গনাথ।ওর সামনে খবরের কাগজের একটা পাতা তেরছা হয়ে পড়ে রয়েছে।আমেরিকা মহাশূন্যে একটা নতুন উপগ্রহ পাঠিয়েছে।ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে গোলাগুলি চলছে। গমের ফলন কম হওয়ায় রাজ্যের কোটা কমিয়ে দেয়া হবে। সিকিউরিটি কাউন্সিলে দক্ষিণ আফ্রিকার কোন সমস্যা নিয়ে গরমাগরম তর্ক-বিতর্ক চলছে। এসবের মধ্যে দৈত্যকার বাজের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওই সাদাকালো বিজ্ঞাপন, নিজস্ব টেরচা অক্ষরের ছাঁদে সবার মনযোগ কেড়ে নিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে- ববাসীর! ববাসীর! অর্শ! অর্শ! বিজ্ঞাপনটি ছেপে বেরোতেই শিবপালগঞ্জ ও আন্তর্জাতিক দুনিয়ার মধ্যে ‘ববাসীর’ এক সফল যোগসূত্র হয়ে দাঁড়াল।
ডাকাতদলের আদেশ ছিল যে রামাধীনের তরফ থেকে একটি টাকার থলি এক বিশেষ তিথিতে বিশেষ স্থানে গিয়ে চুপচাপ রেখে আসতে হবে।ডাকাতির এই মডেল এখনও দেশের কোথাও কোথাও বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু এই মডেলটি মধ্যযুগের, কারণ তখন এসব রূপোর বা নিকেলের সিক্কা চলত যা থলি বা বটুয়ায় রাখা হত। আজকাল টাকা কাগুজে রূপ ধারণ করেছে। পাঁচহাজার টাকা তো প্রেমপত্রের মত একটা খামে ভরে কাউকে দেয়া যায়। দরকার পড়লে একটা চেক কেটে দিলেও হয়। তাই ‘ পরশু রাত্তিরে অমুক টিলার উপরে একটা পাঁচহাজার টাকার থলি রেখে চুপচাপ কেটে পড়’ গোছের আদেশ পালন করা বাস্তবে বেশ অসুবিধেজনক। যেমন টিলার উপর খামে ভরে ছেড়ে আসা নোটগুলো এতোল বেতোল হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে।খামের ভেতরের জাল চেক হতে পারে। সংক্ষেপে বললে, শিল্প-সাহিত্য-প্রশাসন-শিক্ষার মত ডাকাতির ক্ষেত্রেও মধ্যযুগীন কায়দাকানুন থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ অনেক সমস্যা তৈরি করতে পারে।
যাই হোক, ডাকাতের দল এতশত ভাবেনি, বোঝাই যাচ্ছে।কারণ যারাই রামাধীনের বাড়িতে ডাকাতির আগাম চিঠি পাঠিয়েছিল তারা কেউ আসল ডাকাত নয়। ইদানীং গ্রাম-সভা আর কলেজের রাজনীতির বখেড়ায় রামাধীন ভীখমখেড়ভী এবং বৈদ্যজীর মধ্যে আকচাআকচি বেড়ে গেছল। এটা যদি শহর হত এবং পলিটিক্স একটু হাই-লেভেলের হত, তাহলে এতদিনে কোন মহিলা থানায় গিয়ে রিপোর্ট লেখাত যে রামাধীনবাবু ওঁর শীলভঙ্গ করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মহিলার সাহস ও সক্রিয় প্রতিরোধের সামনে হার মেনেছেন। এবং মহিলাটি তাঁর শীল পুরোপুরি আস্ত রেখে সোজা থানায় পৌঁছে গেছেন। কিন্তু জায়গাটা এখনও গ্রাম বটেক, তাই রাজনীতির যুদ্ধে ‘শীলভঙ্গ’ নামক অস্ত্রটি এখনও হ্যান্ড গ্রেনেডের সম্মান পায়নি। তাই ডাকাতির ধমকিভরা চিঠি গোছের পুরনো কৌশল অবলম্বন করে রামাধীনকে ক’দিন জ্বালাতন করার চেষ্টা- এই আর কি।
ডাকাতির চিঠিটা যে জালি এটা সবাই জানে। মানে, পুলিশ, রামাধীন এবং বৈদ্যজীর পুরো দরবার- সবাই। আগেও এ’রম চিঠি অনেকবার অনেকের কাছে এসেছে। তাই অমুক তারিখে তমুক সময় টাকা নিয়ে টিলায় পৌঁছতেই হবে -রামাধীনের এমন কোন চাপ ছিলনা। চিঠিটা নকল না হয়ে আসল হলেও রামাধীন চুপচাপ টাকা পৌঁছে দেয়ার বান্দা নয়, তার চেয়ে ঘরে ডাকাত পড়ুক, সেই ভাল।কিন্তু থানায় রিপোর্ট লেখানো হয়ে গেছে, ফলে পুলিশেরও কর্তব্যবোধ জেগে উঠল।কিছু না কিছু করতেই হবে।
সেই বিশেষ দিনে গাঁ থেকে টিলা পর্য্যন্ত স্টেজ পুলিশকে সঁপে দেয়া হল। ওরা চোর-পুলিশ খেলতে লেগে গেল। টিলার মাথায় তো যেন একটা থানা খুলে গেল। ওরা আশপাশের পড়তি ফাঁকা জমি, পাথুরে রুক্ষ এলাকা, জংগল, খেত-খামার, ঝোপঝাড় সব খুঁজে দেখল, কিন্তু ডাকাতদের টিকিটি দেখা গেল না। ওরা টিলার পাশে গাছের ঘন ডালপালা নেড়ে দেখল, খ্যাঁকশেয়ালের গর্তে সঙীন দিয়ে খোঁচা মারল, আর সমতলে নিজের চোখে কটমটিয়ে দেখে বুঝে গেল যে ওখানে যারা আছে তারা ডাকাত নয়, বরং পাখির ঝাঁক, শেয়ালের পাল ও বিবিধ পোকামাকড়।রাতের একপ্রহরে কিছু প্রাণীর সমবত চিৎকারে চটকা ভাঙলে ওরা আশ্বস্ত হল,-- ডাকাত নয়, হুক্কাহুয়া। আর পরে ঝটপট ঝটপট,-- পাশের বাগবাগিচায় বাদুড়ে ফল ঠোকারাচ্ছে। সেই রাতে ডাকাত দল এবং বাবু রামাধীনের মধ্যেকার কুস্তি ১-১ ড্র হল। কারণ টিলায় ডাকাতেরা কেউ আসেনি, রামাধীনও টাকার থলি নিয়ে যায়নি।
থানার ছোট দারোগাটি সদ্য চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। টিলায় চড়ে ডাকাত ধরার কাজ ওনাকেই দেয়া হয়েছিল। উনি ভেবেছিলেন মাকে নিয়মকরে প্রতিসপ্তাহে পাঠানো চিঠির আগামী কিস্তিতে লিখবেন—‘ মা, ডাকাতের দল মেশিনগান চালিয়েছিল; ভয়ংকর গোলাগুলি । তবু মা তোমার আশীর্বাদে আমার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি’।
কিন্তু কিছুই হলনা। রাত্তির একটা নাগাদ উনি টিলা থেকে সমতলে নেমে এলেন। ঠান্ডা বেড়ে গেছল। অমাবস্যার ঘন অন্ধকার। আর ওঁর মনে জেগে উঠল নগরবাসিনী প্রিয়ার জন্যে আকুলিবিকুলি। উনি ছিলেন হিন্দি সাহিত্যে স্নাতক। এতসব কারণ মিলে ওঁর গলায় গান এল; প্রথমে গুনগুনিয়ে তাদারোগারপর স্পষ্ট সুরে—‘হায় মেরা দিল! হায় মেরা দিল’!
এবার “তীতর কে দো আগে তীতর, তীতর কে দো পীছে তীতর” প্রবাদের মত আগে দু’জন, পেছনে দু’জন সেপাই নিয়ে ছোট দারোগা চলেছেন। দারোগার গানের সুর চড়ছে দেখে সেপাইরা ভাবছে- ঠিক আছে, ঠিক আছে; নতুন নতুন ডিউটিতে এসেছেন, ক’দিন বাদে লাইনে এসে যাবেন।খোলা ময়দান পেরিয়ে যেতে যেতে দারোগার গলা আর উদাত্ত হল। বোঝা গেল, যে নেহাত বোকা বোকা কথাগুলো মুখ ফুটে বলতে লজ্জা করে সেগুলো নিয়ে দিব্যি গান গাওয়া যায়।
রাস্তা প্রায় এসে গেছে। তখনই একটা বড়সড় গর্ত থেকে আওয়াজ এল- কর্ফৌন হ্যায় সর্ফালা?
দারোগার হাত কোমরের রিভলভারে চলে গেল। সেপাইরা হকচকিয়ে গেল। তখন গর্ত থেকে আবার শোনা গেল- কর্ফৌন হ্যায় সর্ফালা?
এক সেপাই দারোগার কানে ফুসফুসিয়ে বলল—গুলি চলতে পারে। গাছের আড়ালে সরে যাই হুজুর?
গাছের আড়াল প্রায় পাঁচগজ দূরে। দারোগা সেপাইয়ের কানে ফুসফুস করে বললেন-তোমরা গাছের আড়ালে যাও; আমি দেখছি।
এবার উনি বললেন- ‘গর্তের ভেতরে কে? যেই হও, বাইরে বেরিয়ে এস’। তারপর একটি সিনেমার স্টাইলে বললেন-‘তোমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। আর আধমিনিটের মধ্যে না বেরিয়ে এলে গুলি চালাব’।
গর্তের থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। তারপর হঠাৎ শোনা গেল- মর্ফর গর্ফয়ে সর্ফালে, গর্ফোলি চর্ফলানেওয়ালে!
[এসব শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরে ‘র্ফ’ বাদ দিয়ে পড়লেই মানে স্পষ্ট হবে—মর গয়ে সালে, গোলি চলানেওয়ালে! ঠিক ছোট মেয়েরা যেমন নিজেদের মধ্যে ‘চি’ জুড়ে কোড বানিয়ে কথা বলে। লাভার বলতে হলে বড়দের সামনে বলে-চিলাচিভাচির।]
প্রত্যেক ভারতীয় ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোলে ভাষার মারপ্যাঁচে্র মুখোমুখি হলে নিরেট আকাট হয়ে যায়। এতরকম আঞ্চলিক কথ্যভাষা বা বুলি ওদের কানের পরদায় আছড়ে পড়ে যে ওরা খানিকবাদে হার মেনে ভাবে—হবে নেপালি কি গুজরাতি!এই ভাষাটাও ছোট দারোগাকে নাজেহাল করে দিল। উনি ভাবতে লাগলেন -ব্যাপারটা কী? এটুকু বঝা যাচ্ছে যে কেউ গালি দিচ্ছে। কিন্তু কোন ভাষায় দিচ্ছে কেন বোঝা যাচ্ছে না?
বোঝাবুঝির পালা শেষ হলে যে গুলি চালাতে হয় এই আন্তর্জাতিক নীতিটি ওনার ভাল করে জানা আছে। তাই শিবপালগঞ্জে ওই নীতি প্রয়োগ করবেন ভেবে উনি রিভলবার বাগিয়ে হেঁকে উঠলেন—“গর্তের বাইরে বেরিয়ে এস, নইলে এবার গুলি চালাব’।
কিন্তু গুলি চালানোর দরকার হলনা। এক সেপাই গাছের আড়ালা থেকে বেরিয়ে এসে বলল-হুজুর, গুলি চালাবেন না যেন। এ ব্যাটা জোগনাথওয়া, মাল টেনে গাড্ডায় পড়ে গেছে।
সেপাইয়ের দল মহোৎসাহে গর্তের চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। দারোগা বললেন—জোগনাথওয়া? সেটা আবার কে?
এক পুরনো সেপাই বলল—এ হল শ্রীরামনাথের পুত্র জোগনাথ, একলা মানুষ, তবে একটু বেশি মাল টানে।
সবাই মিলে জোগনাথকে টেনেটুনে দাঁড় করালো, কিন্তু যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় না, তাকে অন্যেরা কতক্ষণ ধরে রাখবে! তাই ও ল্যাগব্যাগ করে পড়ে যাচ্ছিল, একবার সামলানো হল তারপর ও গর্তটা উপর পরমহংসের মত বসে পড়ল। এবার ও বসে বসে চোখ মিটমিট করে হাতটাত নেড়ে একবার বাদুড় আর একবার শেয়ালের মত আওয়াজ বের করে একটু মানুষের স্তরে নেমে এল, কিন্তু ওর মুখ থেকে ফের ওই শব্দ বেরোল-- কর্ফৌন হ্যায় সর্ফালা?
দারোগা জিজ্ঞাসা- এটা আবার কোন বুলি?
সেপাই বলল- বুলি দিয়েই তো চিনলাম যে ব্যাটা জোগনাথ ছাড়া কেউ নয়।ও ‘সর্ফরী’' বুলি কপচায়। এখন হুঁশ নেই তাই গাল পাড়ছে।
যোগনাথের গাল পাড়ার প্রতি নিষ্ঠা দেখে দারোগা প্রভাবিত হলেন। বেহুঁশ অবস্থায়ও কিছু না কিছু করছে তো! উনি ওর ঘেঁটি ধরে ঝটকা মেরে বললেন- হোশ মে আও। হুঁশ ফিরে আসুক ব্যাটার।
কিন্তু জোগনাথ হুঁশ ফেরাতে চায় না যে!খালি বলল-সর্ফালে!
সেপাইয়ের দল হেসে উঠল। ওকে চিনত যে সেপাই, সে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচাল—জর্ফোগনাথ, হর্ফোশ মেঁ অর্ফাও! জোগনাথ, হোশ মেঁ আও।
এতেও জোগনাথের কোন হেলদোল নেই; কিন্তু ছোট দারোগা এবার সর্ফরী বুলি শিখে ফেললেন।মুচকি হেসে টিপ্পনি করলেন—এই শালা আমাদের সবাইকে শালা বলছে যে!
উনি দু’ঘা দেবেন ভেবে যেই হাত তুললেন অমনই একজন সেপাই ওনাকে থামিয়ে দিয়ে বলল-যেতে দিন হুজুর, যেতে দিন।
সেপাইদের এতটা মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ দারোগাবাবুর খুব একটা পছন্দ হলনা।উনি তামাচা মারতে উদ্যত হাত সামলে নিলেন কিন্তু আদেশের স্বরে বললেন- ব্যাটাকে নিয়ে চল আর হাজতে পুরে দাও।ধারা ১০৯ এর কেস ঠুকে দাও।
জনৈক সেপাই বলে উঠল—এটা ঠিক হবেনা হুজুর!ওর এ’ গাঁয়েই বাস। দেয়ালে রঙ দিয়ে বিজ্ঞাপন লেখে। কথায় কথায় সর্ফরী বুলি ঝাড়ে। ব্যাটা বদমাশ বটে, কিন্তু দেখনদারির জন্যে কিছু-না-কিছু কাজটাজ করতেই থাকে।
ওরা জোগনাথকে মাটির থেকে টেনে তুলে কোনরকমে পা চালাতে বাধ্য করে রাস্তার দিকে এগোয়। দারোগা বললেন,’ বোধহয় দারু খেয়ে গালি দিচ্ছিল। কোন-না-কোন ধারা ঠিক লেগে যাবে।এখন তো ব্যাটাকে লেন
সেপাইটি নাছোড়বান্দা। ‘কেন যে হুজুর খামোখা ঝঞ্ঝাট বাড়াচ্ছেন!কী লাভ! গাঁয়ে পৌঁছে ওকে এখন ওর ঘরে এক ধাক্কায় ঢুকিয়ে দিয়ে তবে ফিরব।একে হাজতে পুরবেন কী করে?জানেনই তো, ও হল বৈদ্যজীর লোক।
ছোট দারোগা চাকরিতে সবে এসেছেন, কিন্তু সেপাইদের মানবতাবাদী ভাবনার আসল কারণটা উনি চটপট বুঝে ফেললেন। সেপাইদের থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে পেছন পেছন চলতে চলতে উনি ক্রমশঃ ঘোর অন্ধকার, অল্প অল্প শীত নগরে বিনিদ্র রাতজাগা প্রিয়া এবং ‘হায় মেরা দিল’ গুনগুনিয়ে ক্রমশঃ শান্ত হলেন।



.jpeg)

.jpeg)

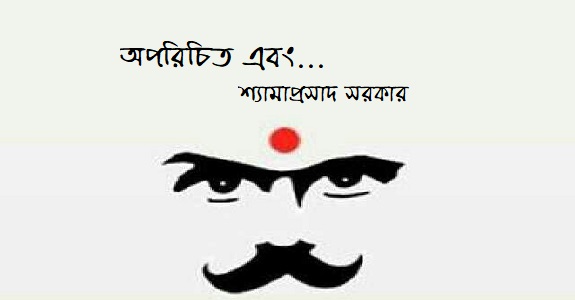










0 comments: