অধ্যায়-২
শিবপালগঞ্জ থানাতে একটি লোক দারোগাজীকে বলছে--- "আজ-কাল করতে করতে অনেক দিন গড়িয়ে গেছে হুজুর! আমার চালান পেশ করতে আর দেরি করবেন না।"
এই আরামকেদারাটি বোধ্হয় মধ্যযুগীন কোন সিংহাসন ছিল, ঘষে ঘষে আজ এই হাল। দারোগাজী ওতে বসে ছিলেন, আবার শুয়েও ছিলেন। এমন কাতর আবেদন শুনে মাথা তুলে বললেন," চালানও হয়ে যাবে, তাড়া কিসের? কিসের বিপদ?"
লোকটি আরামকেদারার পাশে পড়ে থাকা একটি প্রাগৈতিহাসিক মোড়ায় চেপে বসে বলতে লাগল," আমার জন্যে তো সমূহ বিপদ। আপনি আমায় চালান করে দিন, তো ঝঞ্ঝাট মিটে যায়।"
দারোগাজী গুজগুজ করতে করতে কাউকে গালি দিতে লাগলেন। একটু পরে বোঝা গেল যে উনি বলছেন--- কাজের ঠ্যালায় চোখে অন্ধকার দেখছেন। এত কাজ যে অপরাধের তদন্ত হচ্ছে না, মামলার চালান পেশ হচ্ছে না, আদালতে সাক্ষী যাচ্ছে না। এত কাজের বোঝা যে একটা কাজও হচ্ছে না।
মোড়া ঘষটে আরামাকেদারার গা ঘেঁষে এল। বলল, " হুজুর, শত্রুরা বলাবলি করছে যে শিবপালগঞ্জে দিনেদুপুরে জুয়োর আড্ডা বসছে। পুলিস কাপ্তেনের কাছে বেনামী চিঠি গেছে। আর আপনার সঙ্গে তো আমাদের সমঝোতা ছিলই যে বছরে একবার চালান করবেন। এই বছর চালান করতে করতে অনেক দেরি হয়ে গেধ্হে। এই সময় করে ফেলুন, তো লোকের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।"
শুধু আরামকেদারা কেন, সবকিছুই যেন মধ্যযুগের। তক্তপোষটা, ওর ওপরে বিছিয়ে দেয়া ছেঁড়াখোড়া শতরঞ্জি, শুকনো খটখটে দোয়াত,কোনামোড়া আধময়লা রেজিস্টার --- সবগুলো যেন কয়েকশ' বছর আগের থেকে রাখা আছে।
এখানে বসে চারদিকে চোখ ঘোরালেই মনে হবে যেন ইতিহাসের কোন কোণায় দাঁড়িয়ে আছি। এখনো এই থানায় ঝর্ণাকলমের আমদানি হয় নি, তবে খাগের কলম বিদায় নিয়েছে। টেলিফোন আসেনি। অস্ত্রশস্ত্র বলতে কিছু পুরনো রাইফেল, মনে হয় সিপাহীবিদ্রোহের সময় কব্জা করা। এমনিতে সেপাইদের জন্যে অনেকগুলো বাঁশের লাঠি আছে। কবি বলেছেন যে ওগুলো নদী-নালা পেরোতে বা খেঁকি কুকুর ঠ্যাঙাতে বেশ কাজে লাগবে।
থানার জন্যে কোন জীপ-টিপ নেই। তবে বাহন হিসেবে জনাকয় চৌকিদারের আদরে টিঁকে থাকা ঘোড়া আছে। সে তো শেরশাহের আমলেও ছিল।
আগেই বলেছি যে থানার ভেতর ঢুকলেই মনে হবে যেন হুড়মুড়িয়ে কয়েক্শ' বছর পেছনে এসে পড়েছি। আমেরিকান থ্রিলার পড়ার অভ্যেস থাকলে তো প্রথমেই মনে হবে কোথায় আঙুলের ছাপ দেখার আতসকাঁচ, কোথায় ক্যামেরা আর ওয়ারলেসওলা গাড়ি? তার জায়গায় যা যা আছে সেতো বলাই আছে।
আরও আছে--- সামনে তেঁতুলগাছের নীচে বসে একটা আধন্যাংটো ল্যাংগোটপরা লোক, ভাঙ্গের শরব্ত বানাচ্ছে। একটু পরে জানতে পারা যাবে যে একা ওই একটা লোক বিশটা গ্রামের দেখাশুনোর জন্যে আছে। ও যেমন আছে তেমনি অবস্থায় ওখানে বসে বসেই বিশ গাঁয়ের ক্রাইম ঠেকাতে পারে, ঘটনা ঘটে গেলে তার খোঁজখবর করতে পারে, আর কিছু না ঘটলে কিছু করিয়ে দিতে পারে। আতসকাঁচ, ক্যামেরা,কুকুর, ওয়্যারলেস ওর জন্যে নিষিদ্ধ বস্তু। দেখলে কিন্তু থানার পরিবেশ বেশ রোম্যান্টিক আর অতীতদিনের গৌরব নিয়ে মজে থাকার অনুকূল। যেসব রোম্যান্টিক কবি হারিয়ে যাওয়া অতীতের কথা ভেবে ভেবে কষ্ট পান, তাঁদের এখানে কিছুদিন থাকতে বললে ভালো হয়।
তবে জনগণের আশা-ভরসা বলতে থানার ওই দারোগাজী আর তার কুল্যে গোটা দশ-বারো সেপাই। থানাটির অধীনে প্রায় আড়াই থেকে তিনশ' গাঁ; তবু যদি আট মাইলের মধ্যে কোন গাঁয়ে সিঁধ পড়ে তবে জনতা আশা করবে যে এই সেপাইদের মধ্যে থেকে কেউ না কেউ নিঘ্ঘাৎ দেখে ফেলেছে। আর যদি মাঝরাতে বারো মাইলের মধ্যে ডাকাতি হয় তাহলে পুলিশ নিশ্চই ডাকাতদের আগে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবে। এই বিশ্বাসের জন্যেই কোন গাঁয়ে একটা-দুটো বন্দুক ছাড়া কোন হাতিয়ার রাখতে দেয়া হয় নি।
আর ভয় আছে যে গাঁয়ে হাতিয়ার রাখার অনুমতি দিলে ওখানের বর্বর-অসভ্য লোকজন হাতিয়ার চালানো শিখে নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা বাধাবে,খুনজখম শুরু হবে, রক্তের নদী বইবে। আর ডাকাতদের থেকে নাগরিকদের বাঁচানো? সেসব দারোগাজী আর তাঁর দশ-বারো সেপাইয়ের জাদুকরী-ক্ষমতার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।
এঁদের এই ম্যাজিক পাওয়ারের সবচেয়ে বড় প্রমাণ খুনের মামলায় দেখা গেছে। ফলে বিশ্বাস জন্মেছে যে তিনশ' গাঁয়ে কার মনে কার জন্যে ঘৃণা জন্মেছে, কার সঙ্গে কার শ্ত্রুতা, কে কাকে কাঁচা চিবিয়ে খেতে চায়-- তার খুঁটিনাটি খবর আগে থেকেই এদের কাছে আছে। তাই এঁরা আগে থেকেই এমন চাল চালবেন যাতে কেউ কাউকে মারতে না পারে, আর মারলেও চটপট ধরা পড়ে যায়।
কোথাও খুন হলে এঁরা হাওয়ার বেগে অকুস্থলে গিয়ে খুনীকে ধরে ফেলবেন, শবদেহ নিজেদের কাস্টডিতে নেবেন, রক্তে-ভেজা-মাটি হাঁড়িতে ভরে ফেলবেন আর প্রত্যক্ষদর্শীদের এমন দিব্যদৃষ্টি দেবেন যাতে তারা যেকোন আদালতে মহাভারতের সঞ্জয়ের মতন যা ঘটেছে তার হুবহু বর্ণনা করতে পারে।
সংক্ষেপে বলতে গেলে দরোগাজী আর তার সেপাইরা মানুষ নয়, আলাদীনের প্রদীপ থেকে বেরিয়ে আসা দৈত্য। এদের এমনি বানিয়ে রেখে ইংরেজ ১৯৪৭ এ এদেশ ছেড়ে নিজেদের দেশে ফিরে গেছে। তারপরে ধীরে ধীরে রহস্য ফাঁস হল যে এরা দৈত্য নয় মানুষ, আর এমনি মানুষ যারা নিজেরাই দৈত্য বেরিয়ে আসবে এই আশায় প্রদীপ ঘষেই যাচ্ছে।
শিবপালগঞ্জের জুয়াড়ি কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বেরিয়ে গেলে দারোগাবাবু একবার চোখ তুলে চারদিক দেখে নিলেন। সর্বত্র শান্তি। তেঁতুলগাছের নীচে ভাঙ্গ ঘুটতে থাকা ল্যাংগোটছাপ সেপাইটা পাশে স্থাপিত শিবলিঙ্গের ওপর ভাঙ্গের সরবত ঢালছে, জনৈক চৌকিদার ঘোড়ার পাছায় দলাই-মলাই করছে, লক-আপের ভেতর এক ডাকাত জোরে জোরে হনুমান-চালিশা পড়ছে আর বাইরের ফটকে ডিউটিরত সেপাই- সম্ভবতঃ সারারাত্তির জেগে থাকার ফলে---একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে ঢুলছে।
দারোগাবাবু একটা ছোট্ট ভাতঘুম মারবেন বলে খালি চোখ বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন, দেখতে পেলেন রূপ্পনবাবু আসছে। উনি গজগজ করতে লাগলেন-- একটু যে চোখ বন্ধ করব তার জো নেই!
রূপ্পনবাবু ঢুকতেই উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আর 'জনতার সঙ্গে ভদ্র-ব্যবহার সপ্তাহ' অনেক আগে চলে গেলেও উনি বেশ বিনম্র ভাবে হ্যান্ডশেক করলেন। রূপ্পনবাবু বসতে বসতেই শুরু করলেন, " রামাধীনের বাড়িতে লাল কালিতে লেখা চিঠি এসেছে। ডাকাতের দল পাঁচহাজার টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে। লিখেছে অমাবস্যার রাতে দক্ষিণের টিলার ওপরে--"।
দারোগাবাবু মুচকি হেসে বললেন," এতো মশায় বড্ড বাড়াবাড়ি! কোথায় পুরনো দিনে ডাকাতেরা নদী-পাহাড় ডিঙিয়ে এসে টাকা নিয়ে যেত, আর এখন চায় কি ওদের ঘরে গিয়ে টাকা দিয়ে আসতে হবে!"
রূপ্পনবাবু বল্লেন," যা বলেছেন। যা দেখছি এত ডাকাতি না, ঘুষ চাওয়া।"
দারোগাবাবু একসুরে বল্লেন, " ঘুষ, চুরি, ডাকাতি---আজকাল সব এক হয়ে গেছে। ---পুরো সাম্যবাদ।"
রূপ্পনবাবু," আমার বাবাও তাই বলছিলেন।"
--"কী বলছিলেন?"
--" এই, সব সাম্যবাদ হয়ে যাচ্ছে।"
দুজনেই হেসে উঠলেন।
এবার রূপ্পন বললেন, " না, আমি ঠাট্টা করছি না। সত্যি সত্যি রামাধীনের ঘরে এমনি চিঠি এসেছে। বাবা আমাকে তাই পাঠালেন। উনি বলেছেন যে রামাধীন আমাদের বিরোধী হতে পারে, কিন্তু ওকে এমন করে বিরক্ত করা উচিৎ হবে না।"
--" সুন্দর বলেছেন। বলুন, কাকে কাকে বলতে হবে,- বলে দেব।"
রূপ্পনবাবু গর্তে ঢোকা চোখ কুঁচকে খানিকক্ষণ দারোগার দিকে তাকিয়ে রইলেন।
দারোগা চোখ নামান নি। হেসে বল্লেন," ঘাবড়াবেন না। আমি থাকতে ডাকাতি হবে না।"
রূপ্পনবাবু আস্তে আস্তে বল্লেন, " তা জানি। চিঠিটা জাল। আপনার সেপাইদেরও একটু জিগ্যেস করে দেখবেন। হতে পারে ওদেরই কেউ লিখেছে।"
" হতে পারে না। আমার সেপাইগুলোর মধ্যে কেউ লিখতে জানে না। এক-আধটা হয়তো খালি নাম সাইন করতে পারে।"
রূপ্পন আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ওনাকে থামিয়ে দিয়ে দারোগাবাবু বল্লেন," এত তাড়া কিসের? আগে রামাধীন এসে রিপোর্ট তো লেখাক। চিঠিটা তো সামনে আসুক।"
খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ। দারোগাবাবু যেন কি ভেবে বল্লেন," সত্যি বলতে কি আমার তো এর সাথে শিক্ষাবিভাগের কোন সম্পক্ক আছে বলে মনে হচ্ছে।"
-" কি করে"?
-" আরে শিক্ষাবিভাগ-টিভাগ মানে আপনার কলেজের কথাই বলছি।"
এবার রূপ্পনবাবু রেগে গেলেন। " আপনি তো আমার কলেজের পেছনে আদাজল খেয়ে লেগেছেন।"
--" সে যাই বলুন, আমার তো মনে হয় রামাধীনকে ওই ভয়-দেখানো চিঠিটি আপনার কলেজের কোন ছোকরার কীর্তি, আপনি কী বলেন?"
--" আপনাদের চোখে তো সমস্ত ক্রাইম কেবল স্কুলের ছোকরাদের কীর্তি! আপনার সামনে কেউ বিষ খেয়ে মরে গেলেও সেটাকে আপনি আত্মহত্যা না বলে বলবেন যে বিষ-টিষ কোন স্কুলের ছোঁড়াই এনে দিয়েছে।"
--" ঠিক বলেছেন রূপ্পনবাবু! দরকার পড়লে বলব বই কি! আপনি হয়ত জানেন না যে আমি বখ্তাবর সিং এর চ্যালা!"
এরপর শুরু হল সরকারী চাকরি নিয়ে কথাবার্তা--- ঘুরে ফিরে একটাই গান যার ধূয়ো হল সরকারী কর্মচারি আগে কেমন ছিল আর আজকাল কেমন! শুরু হল বখ্তাবর সিং এর গল্প। এক বিকেলে দারোগা বখ্তাবর সিং একা একা বাড়ি ফিরছিলেন। পার্কের পাশে ওনাকে ঘিরে ধরল দুই খাঁটি বদমাশ---ঝগরু আর মঙ্গরু। তারপর দে দনাদন্।
কথা চাপা রইল না, তখন উনি থানায় গিয়ে নিজের ঠ্যাঙানি খাওয়ার রিপোর্ট লিখিয়ে দিলেন।
পরদিন দুটো বদমাশ এসে ওনার পা' জড়িয়ে ধরল। বল, " হুজুর আমাদের মা-বাপ! বাচ্চা যদি রাগের মাথায় মা-বাপের সঙ্গে বেয়াদপি করে বসে তখন তাকে মাপ করে দেয়াই দস্তুর।"
বখতাবর মা-বাপের কর্তব্য করে ওদের মাপ করে দিলেন। ওরাও ছেলের কর্তব্য পালন করে ওনার বুড়োবয়সের খাওয়া-পরার ভালমত ব্যবস্থা করে দিল।মামলা ভালয় ভালয় মিটে গেল।
কিন্তু পুলিস কাপ্তেন রেগে কাঁই, ইরেংজ যে!
রেগেমেগে বখতাবর সিং কে বলল," টুমি শালা নিজের মামলাটারও ঠিক করে তদন্ত করতে পারলে না,টো অন্যদের কি বাঁচাবে? অন্ধকার ছিল তো কি? কাউকে চিনতে পারোনি? তাতে কি? টুমি কাউকেই চিনতে পারোনি, তো কী? কাউকে সন্দেহ তো করতে পারো! করলে ঠেকাচ্ছে কে?"
তখন বখ্তাবর সিং তিনজনকে সন্দেহের বশে জেলে পুরলেন। তিনজনের সঙ্গেই ঝগরু- মঙ্গরু'র পুরুষানুক্রমে শত্রুতা। ওরা কেস খেল। মামলা চলল। ঝগরু-মঙ্গরু আদালতে বখতাবর সিংয়ের পক্ষে সাক্ষী দিল। কারণ ওরা দেখেছে! হ্যাঁ, ওরা দুজনেই নাকি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে বাহ্য করতে পার্কে ঢুকেছিল। তিন ব্যাটারই জেল হল।
ঝগরু-মঙ্গরুর দুশমনের গতি দেখে পাড়ার বেশ ক'টা ছোকরা রোজ এসে ধর্না দিতে লাগল--" হুজুর! মাই-বাপ! একবার আমাদেরও সুযোগ দিন। আপনাকে ভালো করে প্যঁদাবো। "
কিন্তু বখ্তাবর সিংহ দেখলেন যে বুড়োবয়সের খাওয়াপরার জন্যে ঝগরু আর মঙ্গরুই যথেষ্ট। উনি আর ছেলেপুলের সংখ্যা বাড়াতে চাইলেন না।
গল্পটা শুনে রূপ্পনবাবু খুব হাসলেন। দারোগাবাবু খুশি - একটা চুটকি গপ্পেই রূপ্পনবাবু কাত। আর দরকার নেই। বাকি চুটকিগুলো অন্য লিডারদের হাসাতে কাজে লাগবে। হাসি ফুরোলে রূপ্পন বল্লেন,-" তো আপনি সেই বখ্তাবর সিংয়ের চেলা?"
--" ছিলাম। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে। কিন্তু এখন তো আমরা জনগণের সেবক। আমাদের গরীবের দুঃখকষ্টের ভাগ নিতে হবে। নাগরিকদের ---"।
রূপ্পন দারোগার হাতে খোঁচা মেরে বললেন," ওসব ছাড়ুন, এখানে শুধু আপনি আর আমি, আপনার বক্তিমে শুনবে কে?"
কিন্তু দারোগা দমার পাত্র ন'ন। বলতে লাগলেন," বলছিলাম কি আজাদীর আগের যুগে বখ্তাবর সিংয়ের চেলা ছিলাম। এ যুগে আপনার পিতাশ্রীর চেলা হয়েছি।"
রূপ্পনবাবু সৌজন্য দেখিয়ে জবাব দিলেন," এটা আপনার মহত্ব, নইলে আমার বাবা এমন কি তালেবর?"
এবার উনি গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। রাস্তার দিকে চোখ যেতে বল্লেন," দেখুন তো,মনে হচ্ছে রামাধীন এদিকেই আসছে, আমি চলি। ওই ডাকাতির চিঠিটা একটু ভাল করে দেখে নেবেন কিন্তু।"
রূপ্পনবাবুর বয়স আঠেরো। পড়ছেন ক্লাস টেন এ। পড়তে , বিশেষকরে ক্লাস টেন এ পড়তে উনি খুব ভালোবাসেন। তাই গত তিনবছর ধরে একই ক্লাসে রয়েছেন।
উনি লোক্যাল নেতা। যাঁরা ভাবেন যে ইন্ডিয়াতে রাজনৈতিক নেতা হতে গেলে অনেক অভিজ্ঞতাও পাকাচুল হওয়া দরকার, তাঁরা একবার রূপ্পনবাবুকে দেখুন,--- ভুল ভেঙে যাবে।
উনি নেতা, কারণ উনি সমদর্শী। সবাইকে একই চোখে দেখেন। এটাই ওনার ভিত। ওনার চোখে থানার ভেতরে দারোগা আর লক্ আপের ভেতর চোর-- দুইই সমান।
একই ভাবে, পরীক্ষায় টুকতে গিয়ে ধরা পড়া ছাত্র আর কলেজের প্রিন্সিপাল-- ওনার চোখে এক। উনি সবাইকে দয়ার পাত্র ভাবেন। সবার কাজে লাগেন, সবাইকে কাজে লাগান।
লোকের চোখে ওনার স্থান এমন উঁচুতে যে পুঁজিবাদের প্রতীক দোকানদার ওনাকে জিনিস বেচে না, সমর্পণ করে। তেমনি শোষিতের প্রতীক টাঙ্গাওলা ওনাকে গাঁ থেকে শহরে পৌঁছে দিয়ে ভাড়া চায় না, আশীর্বাদ চায়। ওনার রাজনীতির হাতেখড়ির জায়গা ও রঙ্গমঞ্চ হল ওখানকার কলেজ। সেখানে একশ ছাত্র ওনার আঙুলের টুসকিতে তিল কে তাল বানাতে পারে , আবার দরকার হলে সেই তালগাছে চড়তেও পারে।
উনি রোগাপাতলা, লম্বা গলা, লম্বাটে হাত-পা। কিন্তু লোকে ওনার সঙ্গে সহজে লাগতে চায় না।
জনগণের নেতা হতে গেলে একটু উল্টোপাল্টা পোষাক দরকার বলে উনি ধুতির সঙ্গে রঙিন বুশশার্ট পরে গলায় রেশমি রুমাল বেঁধে ঘুরে বেড়ান। ধুতির কোঁচাটি আবার গলায় জড়ানো। দেখতে উনি একটা মরুটে বাছুরের মত, কিন্তু ঠ্যাকার যেন সামনের দু'পা তুলে চিঁহি করা ঘোড়া।
উনি জন্ম থেকেই জনগণের নেতা, কারন ওর বাপও তাই। ওর বাপের নাম বৈদ্যজী।








.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


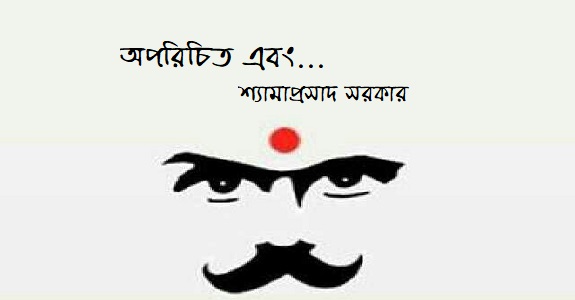











0 comments: