গল্প - মনোজ কর
Posted in গল্পবণিকের মানদন্ড দেখ দিল রাজদণ্ডরূপে
(সময়ানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত বিবরণী)-তৃতীয় অংশ
মারাঠা রাজ্যে তখন পাঁচ সর্দারের মধ্যে তীব্র অন্তর্কলহ। এই পাঁচ সর্দাররা যথাক্রমে পুনার পেশোয়া, নাগপুরের ভোঁসলে, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া ,ইন্দোরের হোলকার এবং বরোদার গায়কোয়াড়। সর্দারদের অভ্যন্তরীণ কলহে দীর্ণ মারাঠা রাজ্যের অবস্থা তখন শোচনীয় বলা যেতে পারে। নানা ফড়নবীশ পেশোয়াকে কার্যত ক্ষমতাহীন করে রেখেছে তখন।১৭৯৫ সালে তৎকালীন পেশোয়া মাধবরাও নারায়ণ মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে মাত্র ২১ বছর বয়সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যায় সমগ্র মারাঠা রাজনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। নতুন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজি রাও নানা ফড়নবীশের হাত থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে জোট বাঁধার চেষ্টা করতে থাকে। এইসময় ১৮০০ সালে নানা ফড়নবীশ পুনাতে দেহত্যাগ করে এবং মারাঠা রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে পৌঁছয়।দৌলত রাও সিন্ধিয়া তখন পেশোয়াকে সমর্থন করলেও হোলকারের সৈন্যসামন্ত মালওয়া অঞ্চলে ব্যাপক লুঠতরাজ চালাতে শুরু করে দিল।নিরুপায় পেশোয়া দ্বিতীয় বাজি রাও অগত্যা ইংরেজদের শরণাপন্ন হলো। ওয়েলেসলি ইতিমধ্যে ভারতে এসে গেছে এবং ভারতীয় রাজ্যগুলির প্রতি ব্রিটিশদের মনোভাব অনেকটাই পাল্টে গেছে। হায়দ্রাবাদের নিজাম ইংরেজদের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতার শর্তাবলী মেনে নিয়েছে। সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স বা অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির মূল কথা হল যে— কোন দেশীয় রাজ্যের রাজা ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবেন । দেশীয় রাজাদের অভ্যন্তরীণ অধিকার ক্ষুন্ন না করে তাঁদের নিজেদের অধীনে রাখাই হল অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির মূল কথা । কোনো দেশীয় রাজা এই নীতি গ্রহণ করলে তাঁকে কতকগুলি শর্ত পালন করতে হত, যেমন—
১) অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ দেশীয় রাজাগুলিকে কোম্পানির বশ্যতা স্বীকার করতে হত ।
২) সংশ্লিষ্ট দেশীয় রাজ্যগুলিতে একদল ইংরেজ সৈন্য এবং একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট রাখতে হত ।
৩) সৈন্যবাহিনীর ব্যয়নির্বাহের জন্য মিত্রতাবদ্ধ রাজ্যকে নগদ টাকা বা রাজ্যের একাংশ ছেড়ে দিতে হত।
৪) কোম্পানির বিনা অনুমতিতে অপর কোনো শক্তির সঙ্গে মিত্রতা বা যুদ্ধবিগ্রহ করা যেত না । অর্থাৎ মিত্র রাজ্যগুলির বৈদেশিক নীতি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নির্ধারণ করত ।
৫) চুক্তিবদ্ধ রাজ্যে ইংরেজ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ইউরোপীয়কে তাড়িয়ে দিতে হত ।
৬) এই সব বশ্যতার বিনিময়ে কোম্পানি সেই রাজ্যকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, বৈদেশিক আক্রমণ এবং অন্যান্য বিপদ থেকে রক্ষা করত ।
হায়দ্রাবাদ এবং মাইসোরের পর মারাঠাদের মুখোমুখি হবার সুযোগ পেয়ে গেল ব্রিটিশ। ১৮০২ সালে হোলকাররা যখন পেশোয়াকে পর্যুদস্ত করে এবং পুনাতে ব্যাপক লুন্ঠন শুরু করলো তখন পেশোয়া ভাসাই পালিয়ে গিয়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করে কার্যত ব্রিটিশদের অধীনতা স্বীকার করে নিল। সুরাত দিয়ে দেওয়া হল কোম্পানিকে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী পেশোয়া দ্বিতীয় বাজি রাওকে পুনার সিংহাসনে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করলো ব্রিটিশ সেনাবাহিনী। কিন্তু মারাঠাদের স্বাধীনতা খর্ব করা গেল না। আসলে এখান থেকেই শুরু হলো দ্বিতীয় ব্রিটিশ-মারাঠা যুদ্ধের। মারাঠা রাজত্ব কুক্ষিগত করার জন্য হোলকার অন্য সর্দারদের সঙ্গে জোট বাঁধার চেষ্টা শুরু করে দিল। অন্যদিকে ওয়েলেসলি এবং লেক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়লো। প্রায় দু’বছর যুদ্ধের পর ১৮০৫ সালে মারাঠা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলকে এবং মারাঠা অধিকৃত অন্যান্য অঞ্চলকেও নিজেদের নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসতে সক্ষম হলো ওয়েলেসলি। রাজপুত, জাঠ, রোহিল্লা এবং উত্তর মালওয়ার বুন্দেলারাও ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রনে এসে গেল। সিন্ধিয়ারাও দিল্লি, আগ্রা, গুজরাট এবং অন্যান্য মারাঠা অঞ্চলকে অধীনতামূলক মিত্রতার আওতায় নিয়ে আসতে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু এতসব কিছু করার পরেও মারাঠা শক্তিকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করা গেল না। বিদ্রোহের আগুন জ্বলতেই থাকলো সর্দারদের মধ্যে।
অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম না হয়ে ব্রিটিশ সরকার ওয়েলেসলিকে ১৮০৫ সালে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। নতুন গভর্নর জেনারেল হয়ে আবার এলো কর্নওয়ালিশ। তাকে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হলো রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকার জন্য। এই সুযোগে হোলকার এবং সিন্ধিয়ারা মালওয়া এবং রাজস্থানের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক লুন্ঠন চালু করে দিল। এভাবেই চলতে থাকলো যতক্ষণ না ১৮১৩ সালে হেস্টিংস ভারতবর্ষে এল নতুন গভর্নর জেনারেল হয়ে। হেস্টিংস এসেই সর্বপ্রধানত্বের নীতি চালু করে। প্যারামাউন্টসি বা সর্বপ্রধানত্বের নীতি অনুযায়ী কোম্পানিই হচ্ছে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং এই ক্ষমতাকে রক্ষা করার জন্য কোম্পানি যে কোনও রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং প্রয়োজনে সেই রাজ্যকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিতে পারে। এইসময় পেশোয়া দ্বিতীয় বাজি রাও আর একবার সর্দারদের সংগঠিত করে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের শেষ চেষ্টা করে। শুরু হয় তৃতীয় ব্রিটিশ মারাঠা যুদ্ধ (১৮১৭-১৯)। এই যুদ্ধে হোলকার এবং পিন্ডারিরা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ব্রিটিশরা পেশোয়া দ্বিতীয় বাজি রাও এর অধীনস্থ সমস্ত অঞ্চল নিজেদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসে এবং পেশোয়া প্রথা চিরতরে বিলুপ্ত করে দেয়। ভোঁসলে এবং হোলকারদের নিয়ন্ত্রনে থাকা বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধীনতামূলক মিত্রতার আওতায় নিয়ে এসে মারাঠা রাজ্যজয় সম্পূর্ণ করে ব্রিটিশরা।
ইতিমধ্যে উত্তর ভারতেও বিভিন্ন অঞ্চল দখলের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। বক্সারের যুদ্ধ এবং এলাহাবাদ চুক্তির পরবর্তী পর্যায়ে অবধ একটি নিরপেক্ষ রাজ্য হিসাবে ব্রিটিশ অধ্যুষিত বাংলা এবং রাজনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত উত্তর ভারতের মধ্যে অবস্থান করছিল। মারাঠাদের হাত থেকে অবধকে রক্ষা করার অছিলায় ব্রিটিশেরা ১৭৭৩ সালে অবধের দরবারে নিজেদের প্রতিনিধি এবং পাকাপাকি ভাবে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী নিয়োগ করে। এই প্রতিনিধি এবং সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব নিতে হয় নবাব সুজাউদ্দৌল্লাকে। এই ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমশ বাড়াতে থাকে ব্রিটিশেরা। ব্রিটিশদের এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য করবৃদ্ধি করতে বাধ্য হয় নবাব সুজাউদ্দৌল্লা। করবৃদ্ধির ফলস্বরূপ তালুকদারদের সঙ্গে সংঘাত বাঁধে নবাবের এবং অবধে সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক অস্থিরতা। এই অস্থিরতার অজুহাতেই পরবর্তীকালে অবধ দখল করে নেয় ব্রিটিশ। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭৪ সালে গভর্নর জেনারেল হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেয় যে খরচের সমপরিমাণ রাজস্ব ব্রিটিশরা নিজেরাই আদায় করে নেবে এবং তার জন্য অবধ রাজ্যের কিছু কিছু অঞ্চল তারা অধিগ্রহণ করবে। মাইসোরের যুদ্ধ এবং ফরাসিদের মোকাবিলায় বিপুল অর্থব্যয়ের কারণে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ে ব্রিটিশদের। সেইসময় অবধের নবাব বেনারসের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছিল। অবধের হাত থেকে বাঁচানোর নামে এই টাকা আদায়ের জন্য বেনারসের রাজা চৈত সিং এর উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে ব্রিটিশেরা। ব্রিটিশদের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে অবশেষে ১৭৮১ সালে ব্রিটিশদের কাছে বেনারসকে গচ্ছিত রাখতে বাধ্য হয় চৈত সিং। ১৭৭৫ সালে নবাব সুজাউদ্দৌল্লার মৃত্যু হয়। সুজাউদ্দৌল্লার বিশাল সম্পদের অধিকারী হয় তার স্ত্রী বেগম উম্মত উজ জাহারা। হেস্টিংসের নির্দেশে ব্রিটিশদের কাছে প্রয়াত সুজাউদ্দৌল্লার ধার মেটানোর জন্য তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ মাসোহারা আদায় করতে শুরু করে ব্রিটিশরা। অবধ অধিগ্রহণের পরিকল্পনা ব্রিটিশদের দীর্ঘদিন ধরেই ছিল। ১৮০১ সালে ওয়েলেসলি এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করে যখন নবাব ওয়াজির আলি খান ব্রিটিশদের চাহিদা মেটোনোর অক্ষমতার কথা সর্বসমক্ষে জানায়। অবশ্য এই অধিগ্রহণের পিছনে অন্যান্য কারণও ছিল। এলাহাবাদ চুক্তির পর নবাব সুজাউদ্দৌল্লা বারবার কোম্পানির কাছে অভিযোগ জানিয়েছিল যে কোম্পানিকে দেওয়া করমুক্ত বাণিজ্যের অধিকারের ব্যাপক অপপ্রয়োগ ঘটাচ্ছে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা এবং তাদের ভারতীয় গোমস্তারা তাদের নিজেদের ব্যবসার জন্য। কোম্পানির অধিকর্তারা এব্যাপারে কিছু পদক্ষেপ নিতে পারেনি।এছাড়াও সমুদ্রপথে বাণিজ্যের জন্য তখন অবধ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। অষ্টাদশ শতাব্দির শেষদিকে লন্ডনে নীলের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই চাহিদার শতকরা ষাট ভাগ আসত অবধ থেকে। অবধের তুলো চিনা বাজারে বিক্রি করা হতো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভারসাম্য ব্রিটিশদের অনুকূলে রাখার জন্য। সুতরাং ১৭৮৮ সালে কর্নওয়ালিশের সঙ্গে অবাধ এবং মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত্বেও রপ্তানির উপর নবাবের কর চাপানোর সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবেই অনভিপ্রেত এবং যথেষ্ঠ বিরক্তির কারণ ছিল। সুতরাং অধিগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো যখন ওয়েলেসলি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের অভিপ্রায় সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছলো।
অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রথম হস্তক্ষেপ করার সুযোগ এল ১৭৯৭ সালে সুজাউদ্দিন এর উত্তরসূরী নবাব আসাফুদ্দৌল্লার দেহান্তের পর। ব্রিটিশরা তার ছেলের নবাবের আসনের দাবি না মেনে আসাফুদ্দৌল্লার ভাই সাদাত আলি খানকে সিংহাসনে বসাল। মূল্যবাবদ সাদাত আলি খান ব্রিটিশদের বেশকিছু অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের অধিকার এবং কয়েক কিস্তিতে বছরে ৭৬ লক্ষ টাকা ভর্তুকি দেবার প্রতিশ্রুতি দিল। নতুন নবাব বছর বছর টাকা দিতে রাজি হলেও তার শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশদের হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে তীব্র আপত্তি জানালো। ব্রিটিশদের আসল উদ্দেশ্য সাধিত হল না। ১৮০১ সালে ওয়েলেসলি নিজের ভাই হেনরিকে পাঠালো সাদাত আলি খানের সঙ্গে ভর্তুকির প্রসঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে। চুক্তির ফলস্বরূপ অর্ধেক অবধ ব্রিটিশদের হাতে চলে গেল। চুক্তি অনুযায়ী এটা ঠিক হলো যে ভর্তুকির টাকা ব্রিটিশরা সরাসরি রাজস্ব হিসাবে রোহিলখন্ড, গোরখপুর এবং দোয়াব থেকে আদায় করে নেবে। বাস্তবে এই তিনটি অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল প্রায় এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা যা ছিল নির্দ্ধারিত ভর্তুকির প্রায় দ্বিগুন। যদিও যুক্তি হিসাবে দেখানো হল যে সাদাত আলি খানের অপশাসন থেকে অবধকে বাঁচাবার জন্য ব্রিটিশরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আসলে এই পদক্ষেপ রাজস্ব এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক চাহিদা ছাড়া আর কিছু নয়। যদিও এই চুক্তি ভর্তুকি আদায় সংক্রান্ত সমস্যার সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করেছিল তবুও ব্রিটিশদের জুলুমের কোনও অন্ত ছিল না। লক্ষ্ণৌ এর ব্রিটিশ রেসিডেন্সি ধীরে ধীরে অবধের ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে উঠতে থাকলো। অর্থ, সামরিক সহযোগিতা এবং নানারকম সুবিধার বিনিময়ে ব্রিটিশরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন দরবার, প্রশাসক এবং জমিদারশ্রেণী তৈরি করে নিল। ক্রমে ক্রমে পরিকল্পিত ভাবে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নবাবকে কার্যত ক্ষমতাশূণ্য করে দিল ব্রিটিশ রেসিডেন্সি। অবশেষে ১৮৫৬ সালে অপশাসনের অজুহাতে লর্ড ডালহৌসি অবধের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রন নিজেদের করায়ত্ত করে নিল। উত্তর ভারত দখল প্রায় শেষ। বাকি রইল কেবল শিখ অধ্যুষিত পাঞ্জাব। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে ১৭৯৫ থেকে ১৭৯৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে রঞ্জিত সিং এর নেতৃত্বে শিখ সম্প্রদায় সংঘবদ্ধ হয়েছিল । রঞ্জিত সিং এর জীবদ্দশায় ব্রিটিশরা পাঞ্জাবের ধারে কাছে আসতে সাহস করেনি। রঞ্জিত সিং এর মৃত্যুর পর পাঞ্জাবে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়। উত্তরাধিকার নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত এবং যুদ্ধের শুরু হয়। রঞ্জিত সিং দীর্ঘ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভারসাম্য সৃষ্টি করে এক পতাকার তলায় সকলকে সমবেত করেছিলেন সেই ভারসাম্য ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে থাকে। এই সুযোগে প্রশাসনের অভ্যন্তরে দুর্নীতি বাসা বাঁধতে থাকে। পাঞ্জাবি এবং ডোগরাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কারদারদের অবাধ লুন্ঠন পাঞ্জাবের অর্থনীতিকে প্রায় ধ্বংস করে দিল। পাঞ্জাবের বিভিন্ন সম্প্রদায় ক্রমাগত একে অপরের থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলো এবং পরিস্থিতি ক্রমশ ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের অনুকূল হয়ে উঠতে শুরু করলো। সংক্ষেপে বলতে গেলে ১৮৩৯ সালে রঞ্জিত সিং মারা যাওয়ার আগে তার ছেলে খড়ক সিংকে উত্তরাধিকার অর্পণ করে যান। খড়ক সিং নিজে দক্ষ প্রশাসক ছিল না এবং বহুলাংশেই তার ডোগরা উজির রাজা ধ্যান সিং এর উপর নির্ভরশীল ছিল। সম্পর্ক প্রথমে ভালো থাকলেও পরবর্তী কালে খড়ক সিং এর ক্ষমতা হ্রাস করার জন্য ধ্যান সিং রাজদরবারে ডোগরা বিরোধীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। ধ্যান সিং তখন যুবরাজ নাও নিহাল সিং এর সঙ্গে জোট বেঁধে ডোগরা বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। কিন্তু এই লড়াই বেড়ে ওঠার আগেই ১৮৪০ সালে খড়ক সিং এর মৃত্যু হয়। তার কিছুদিনের মধ্যেই এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় নাও নিহাল সিং এর মৃত্যু হয়। এমতাবস্থায় সিংহাসনের অধিকার নিয়ে পরিবারের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। একদিকে ছয় জীবিত যুবরাজের একজন যুবরাজ শের সিং অন্যদিকে খড়ক সিং এর পত্নী মহারাণী চাঁদ কাউর। তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে নিহাল সিং এর বিধবা পত্নীর গর্ভস্থ সন্তানের অধিকার দাবি করেন। ডোগরা সম্প্রদায় শের সিং এর প্রতি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করে। অন্যদিকে সিন্ধনওয়ালিয়া সর্দারেরা মহারাণীর পক্ষ নেয়। দু পক্ষই সমর্থন চেয়ে ব্রিটিশদের দ্বারস্থ হয়। ব্রিটিশরা নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। অবশেষে ডোগরাদের চক্রান্তে শের সিং সিংহাসনে বসে এবং উজির ধ্যান সিং এর সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। কিছুদিনের মধ্যেই ধ্যান সিং এর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা হ্রাসের অভিপ্রায়ে শের সিং তার বিরোধীপক্ষের সিন্ধনওয়ালিয়া সর্দারদের সাহায্য প্রার্থনা করে। সিন্ধনওয়ালিয়া সর্দারেরা বৃহত্তর রাজপরিবারের অংশ ছিল।তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সিন্ধনওয়ালিয়া সর্দারেরা ১৮৪৩ সালে শের সিং , শের সিং এর পুত্র এবং রাজা ধ্যান সিংকে হত্যা করে নিজেদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। ধ্যান সিং এর ছেলে রাজা হীরা সিং ডোগরা সেনাবাহিনীর একাংশের সাহায্যে সিন্ধনওয়ালিয়া নেতাদের হত্যা করে রঞ্জিত সিং এর কনিষ্ঠ সন্তান পঞ্চবর্ষীয় দলীপ সিং কে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে উজিরের পদে বসে। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরীণ বিবাদ এবং সর্দারদের পারষ্পরিক শত্রুতা বাড়তেই থাকে। ইতিমধ্যে খালসা সেনাবাহিনী নিজেরা ক্ষমতার কেন্দ্রে এসে পাঞ্জাবের রাজনীতি নিয়ন্ত্রন করতে শুরু করে। শের সিং এর রাজত্বে সেনাবাহিনীর সদস্যেরা ছোট ছোট দল বা পঞ্চায়েত গঠন করে সরাসরি মহারাজের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে। এইসমস্ত পঞ্চায়েতগুলি এখন রাজদরবারে তাদের চাহিদা বাড়াতে থাকে দিনের পর দিন। তাদের চাহিদা না মিটিয়ে হীরা সিং এর পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এইভাবে বেশিদিন চলা সম্ভব নয়। সেনাবাহিনীর মধ্যে ডোগরা বিরোধী মনোভাব বাড়তে থাকে এবং ১৮৪৪ সালে হীরা সিং সেনাবাহিনীর বিক্ষুব্ধ অংশের হাতে নিহত হয়। দলীপ সিং এর মা অর্থাৎ রঞ্জিত সিং এর কনিষ্ঠা স্ত্রী মহারাণী জিন্দন রিজেন্ট নিযুক্ত হয় এবং তার ভাই সর্দার জওয়াহির সিং উজিরের পদে বসে। কার্যত এই দুজনেই সেনাবাহিনীর হাতের পুতুল ছিল। একদিকে খালসা সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক উত্থান এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র নিয়ে তাদের পরিকল্পনা এবং অন্যদিকে লাহোরে কোনও স্থায়ী সরকার না থাকায় ব্রিটিশরা পাঞ্জাব নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ব্রিটিশরা পাঞ্জাবকে একদিকে অধিকৃত উত্তর ভারত এবং অন্যদিকে পার্সিয়া এবং আফগানিস্তানের মুসলমান শাসকদের মধ্যে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছিল। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশরা বুঝতে পারল এই নীতি আর কাজে লাগবে না। ১৮৪০ সাল থেকেই ব্রিটিশরা শিখদের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু করেছিল। ১৮৪৩ সাল থেকে ব্রিটিশরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। ১৮৪৫ সালের সেপ্টেম্বর সেনাবাহিনীর হাতে জওয়াহির সিং এর হত্যার সঙ্গে সঙ্গে লর্ড হার্ডিঞ্জ পাকাপাকি ভাবে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৪৫ শুরু হয় ব্রিটিশদের সঙ্গে শিখদের যুদ্ধ। অসফল যুদ্ধ পরিচালনা এবং কিছু সর্দারদের বিশ্বাসঘাতকার জন্য শিখরা এই যুদ্ধে ব্রিটিশদের কাছে পরাজিত হয়। ১৮৪৬ সালে স্বাক্ষরিত হয় অপমানজনক লাহোর চুক্তি। এই চুক্তি অনুযায়ী জলন্ধর দোয়াবের বিলুপ্তি ঘটে, কাশ্মির দিয়ে দেওয়া হয় ব্রিটিশ তাঁবেদার জম্মুর রাজা গুলাব সিংকে। লাহোর সেনাবিহিনীর সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে সেখানে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী বসানো হয়। দলীপ সিংকে সিংহাসনে রাখা হলো কিন্তু অভিবাবকের আসনে বসানো হলো ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে।মহারাণী জিন্দানকে সরানো হল রিজেন্ট পদ থেকে এবং ব্রিটিশ প্রতিনিধির হাতে সমস্ত বিভাগের সমস্ত সিদ্ধান্ত নেবার একচ্ছত্র অধিকার দেওয়া হলো। রাজা এবং রাজমাতার ভূমিকা কেবলমাত্র প্রতীকী হয়ে রইল। যেহেতু ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য ছিল পাঞ্জাবকে সামগ্রিক ভাবে নিজেদের করায়ত্ত করা সেইজন্য ১৮৪৯ সালে দ্বিতীয় ব্রিটিশ- পাঞ্জাব যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই বিদ্রোহী মুলতানের গভর্নর দিওয়ান মুল রাজ, আটারিওয়ালার গভর্নর সর্দার ছত্তর সিং এবং তার পুত্র হরিপুরের রাজা শের সিংকে দমন করার অজুহাতে সমগ্র পাঞ্জাব নিজেদের অধিকারে নিয়ে নিল ব্রিটিশরা। ১৮৪৯ সালের ২৯শে মার্চ মহারাজা দলীপ সিং পাঞ্জাবের স্বাধীনতা ব্রিটিশদের হাতে তুলে দিয়ে পাঞ্জাবকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত করার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলো। বিদ্রোহী সর্দারদের একে একে ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনও উপায় রইলো না।
উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলগুলিও ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রনে আসতে থাকল। কোম্পানি অধিকৃত এই সাম্রাজ্যের নিরাপত্তাজনিত কারণে ব্রিটিশ আগ্রাসন আরও তীব্র আকার ধারণ করলো। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সামরিক আধিকারিকেরা দেশের বাইরে এবং ভিতর থেকে আক্রমণের আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে যত্রতত্র সামরিক ক্ষমতাপ্রদর্শনের নেশায় মেতে উঠলো। এই নিরাপত্তাজনিত আশঙ্কার কারণেই আগ্রাসন সংক্রান্ত ব্রিটিশ সরকারের এবং লন্ডনের কোম্পানি কর্তাদের সমস্ত বিধিনিষেধ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ১৮২৩ সালে আমহার্স্ট যখন ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসে তখন তার প্রতি নির্দেশ ছিল যে ভারতবর্ষে ব্যয়সাপেক্ষ রাজকীয় যুদ্ধ এবং আগ্রাসনের প্রক্রিয়া বন্ধ করে যেন শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু ভারতে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বর্মা থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠলো। বর্মার রাজশক্তি অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে ক্রমে ক্রমে পেগু, তেনাসেরিম এবং আরাকানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করে নেয়। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে মণিপুর, কাছার এবং আসামে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে। এতদিন বর্মার এইসমস্ত কাজকর্মকে কোম্পানির কর্তারা খুব একটা আমল দেয়নি। কিন্তু এখন ব্রিটিশ সামরিকবাহিনী এলাকাদখলের নেশায় উন্মত্ত। তারা যুক্তি খাড়া করলো যে বর্মার এই আগ্রাসন থেকে অভ্যন্তরীণ শত্রুরা সাহস সঞ্চয় করছে। বিপদের সম্ভাবনা সমূলে বিনষ্ট করার জন্য বর্মাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া খুব দরকার। ১৮২৪ সালে শুরু হলো প্রথম বর্মা যুদ্ধ। আসাম, নাগাল্যান্ড এবং বর্মা অধিকৃত আরাকান এবং তেনাসেরিম ব্রিটিশরা দখল করে নিল। ১৮৩০ সালে কাছার এবং ১৮৩৪ সালে বেন্টিঙ্কের আমলে কুর্গও ব্রিটিশদের দখলে এসে গেল। বর্মা যেমন উত্তর-পূর্ব ভারতে তেমনই রাশিয়া ছিল উত্তর-পশ্চিমে ভয়ের কারণ। সুতরাং উত্তর-পশ্চিমেও আগ্রাসনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। অকল্যান্ডের নেতৃত্বে ১৮৩৮ থেকে ১৮৪২ অবধি চলে আফগান যুদ্ধ। ১৮৪২ সালে ব্রিটিশরা নিজেদের অনুগত রাজাকে সিংহাসনে বসিয়ে আফগানিস্থানকে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের অধীনে নিয়ে আসে। এলেনবরো ১৮৪৩ সালে সিন্ধ দখল করে। কিন্তু ঔপনিবেশিক আগ্রাসন চূড়ান্ত রূপ নেয় ডালহৌসির সময় (১৮৪৮ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত)। ব্রিটিশ প্রবর্তিত স্বত্ববিলোপ নীতির আশ্রয় নিয়ে অনেক রাজ্যকেই সরাসরি নিজেদের আওতায় নিয়ে আসে ডালহৌসি। এই নীতি অনুযায়ী যদি কোনও রাজা কোনও পুরুষ উত্তরাধিকারী না রেখে দেহত্যাগ করে তাহলে সেই সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ ব্রিটিশদের হাতে সরাসরি চলে আসবে। এই নীতি ব্যবহার করে ১৮৪৮ সালে সাতারা, ১৮৫০ সালে সম্বলপুর এবং বাঘাট, ১৮৫২ সালে উদয়পুর, ১৮৫৩ সালে নাগপুর এবং ১৮৫৪ সালে ঝাঁসি দখল করে নেয় ব্রিটিশেরা। ১৮৫২-৫৩ সালে দ্বিতীয় বর্মা যুদ্ধ জয় করে পেগু দখল করে ব্রিটিশবাহিনী। সেনাবাহিনীর খরচ আদায়ের জন্য ১৮৫৩ সালে হায়দ্রাবাদ থেকে বেরার বিচ্ছিন্ন করে অধিগ্রহণ করে নেয় ব্রিটিশেরা। ১৮৫৭ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের ৬৩ শতাংশ অঞ্চল এবং ৭৮ শতাংশ জনগণ সরাসরি ব্রিটিশদের অধীনে চলে আসে। বাকি অঞ্চলগুলি ইংরেজদের অনুগত রাজাদের অনুশাসনেই থাকে। ব্রিটিশরা এইসময়ে সরাসরি অধিগ্রহণের পথ ছেড়ে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের পথ বেছে নেয়। খাতায় কলমে স্বশাসিত হলেও আসলে এইসমস্ত রাজারা ছিল ব্রিটিশদের তাঁবেদার এবং প্রতি পদক্ষেপে ব্রিটিশদের হস্তক্ষেপ তাদের একরকম পুতুল করে রেখেছিল।
অবাধ এবং মুক্ত বাণিজ্যের প্রয়োজনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং অধিগ্রহণ শুরু হলেও শেষ অবধি ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত করে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলই হয়ে ওঠে তাদের মূল লক্ষ্য। কিন্তু ভারতবর্ষের মত এক বিশাল দেশকে সম্পূর্ণ নিজেদের অধীনে নিয়ে আসা সহজসাধ্য ছিলনা। সেই সময় নানা কারণে মোগলেরা দূর্বল হয়ে পড়েছিল কিন্তু যে সমস্ত অন্য রাজ্যেরা সেই সুযোগে সিংহাসন দখলের চেষ্টা করছিল তারা কিন্তু খুব একটা দূর্বল ছিল না। প্রচুর সংখ্যক সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র ছিল এই সব রাজ্যের কাছে যদিও আধুনিকতার নিরিখে এই সব অস্ত্রশস্ত্র ব্রিটিশদের চাইতে অনেক নিম্নমানের ছিল। পৃথিবী জুড়ে ব্রিটিশ এবং ফরাসিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তখন বেড়েই চলেছে। সেই কারণে ভারতে অভূতপূর্ব মাত্রায় ব্রিটিশ সৈন্যের সংখ্যা বাড়তে থাকলো। তবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো এই সময় ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে ভারতীয়দের ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিল। ব্রিটিশ অফিসারদের দ্বারা প্রশিক্ষিত নতুন সেনাবাহিনী ব্রিটিশদের প্রতিপক্ষ রাজ্যগুলিকে শায়েস্তা করার কাজে নিযুক্ত করা হলো। এই বিশাল সেনাবাহিনীর সাহায্যে ব্রিটিশরা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলো এবং অধীনতামূলক মিত্রতার অধীন রাজ্যগুলির থেকে আর্থিক চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য সীমান্ত সুরক্ষিত রাখা ব্রিটিশদের কাছে আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল। সীমান্ত সুরক্ষিত রাখার জন্য সরাসরি রাজ্য দখল করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। চলতে থাকলো একের পর এক রাজ্য দখলের যুদ্ধ। রাজস্বের বেশিরভাগ অংশই খরচ হয়ে যেত যুদ্ধে এবং সেনাবাহিনীর ভরণপোষণে। পরিকল্পিত ভাবে অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃশত্রুর থেকে আক্রমণের আশঙ্কা সৃষ্টি করে এই বিপুল সেনাবাহিনীকে সবসময়ে যুদ্ধে নিযুক্ত রাখা হতো।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল অর্থ এবং রসদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাদের প্রতিপক্ষ রাজ্যগুলির থেকে এগিয়ে থাকা। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সৈন্যদের খাওয়া, থাকা এবং নিয়মিত বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে ব্রিটিশরা কোনও কার্পণ্য করতো না। এছাড়াও ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেশীয় রাজাদের চাইতে ব্রিটিশদের বেশি বিশ্বাস করতো। প্রয়োজনে ব্যাঙ্কগুলির থেকে টাকা ধার পেতে ব্রিটিশদের কোনও অসুবিধে হতো না। যেহেতু রাজ্যগুলিকে সরাসরি দখল করে রাজস্ব আদায় ব্রিটিশরা নিজেরাই করতে থাকল সেইজন্য ব্যাঙ্কের উপর নির্ভরতাও ক্রমাগত কমে যেতে থাকলো। পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকা রাজ্যগুলি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে থাকলো। সমস্ত দেশজুড়ে কায়েম হতে থাকলো ব্রিটিশরাজ। রাজ্যশাসন এবং রাজস্ব আদায় দুইই এখন সরাসরি কোম্পানির হাতে । রাজস্ব আদায়, বাণিজ্য এবং সামরিক অভিযান ভারতবর্ষে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনের জন্য একইসূত্রে গ্রথিত ছিল।
অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যান্ড ছিল বিশ্বের ধনী দেশগুলির অন্যতম। অন্য ধনী দেশগুলি যখন সাম্রাজ্যবিস্তারে ব্যস্ত ব্রিটিশ শাসকেরা যুদ্ধের পথে সাম্রাজ্যবিস্তারের পথে না গিয়ে বিশ্বব্যাপী মুক্ত এবং অবাধ বাণিজ্যের পথ অবলম্বন করে। ব্রিটিশ সরকার দেশের বড় কোম্পানিগুলিকে অন্যদেশে বাণিজ্যবৃদ্ধির অনুমতি দেয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে বাণিজ্যবৃদ্ধির অনুমতি পায়। বিনিয়োগ এবং বাজার দখলই ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এই সম্পদবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় সরকার ছিল কোম্পানির অন্যতম সহযোগী। কোম্পানি এবং সরকারের যুগলবন্দী সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যবৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের প্রয়োজনে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত করে। বাজার দখল দিয়ে শুরু করে গোটা দেশকেই দখল করে নেয় ব্রিটিশ।

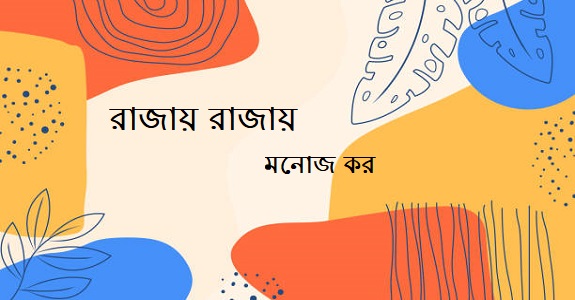









0 comments: