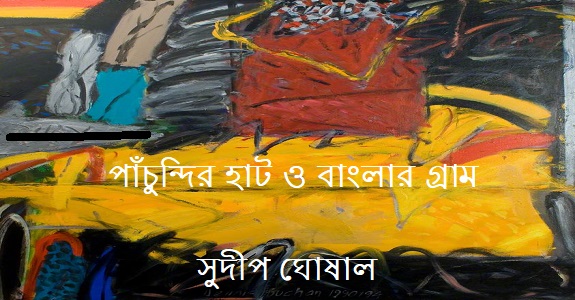শ্মশানের জমিটা ঘাসে ঢেকে আছে। ছোটছোট গর্তে সকালের বৃষ্টিজমা জল। ব্যাঙ লাফিয়ে বেড়াচ্ছে দেদার। জমির পুবে তালপুকুরের পাড়, উত্তরের ঝোপঝাড় আর বাঁশবন ছুঁয়ে চলে গেছে মোরাম ফেলা বড় রাস্তা। রাস্তার উল্টোদিকের ঝুরো বটগাছ, আর গাছের ওপারে ডোমদীঘির কালো জল। বিকেলের রঙ নীলচে সবুজ।
দাদুর সাথে এসে বসি ওই বটের তলায়, শ্মশানের দিকে স্থির চেয়ে থাকে দাদু। দাদুর বাবা সূর্যনারায়ণ, তার বাবা সহদেব, তার বাবা এবং তার আর তারও আগের সব পুরুষের চলে যাওয়া দেখেছে এই সবুজ জমি, তালপুকুর, ডোমদীঘি আর ওই রাস্তা। চোদ্দপুরুষের সালতামামি লেখা আছে এই বংশের খেরোর খাতায়, দলিলে, পাট্টায়।
কোনও এক অখ্যাত দিনে এই গ্রামে এসেছিল আমাদের পূর্বজ, খড় মাটি বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়েছিল আমাদের প্রথম বসত। জমিজিরেত, ঠাকুর দেবতার নামে কাটা হয়েছিল মন্দিরের ভিত, শিকড় চারিয়ে যাচ্ছিল মূল, আমাদের শাখাপ্রশাখারা বাড়ছিল ডালপালায়।
চৈতন্যদেব যখন দন্ডভুক্তির রাস্তা ধরে পৌঁছে যাচ্ছিলেন শ্রীক্ষেত্র তখনই কোনও এক মেঠোপথ ধরে রাস্তায় হাঁটছিল আমার পূর্বপুরুষ, পূর্বনারী আর তাদের বংশজ সন্তানরা। জাতিতে সদগোপ, পেশায় চাষী পেয়েছিল মল্লভূমের রাজস্ব আদায়ের ঠিকা। ডোম বাগদী দুলেরা ছিল তাদের সেপাই। কিন্তু তার আগে? তার, তার কিংবা তারও আগে কোন পাটক, বাটক কিংবা নগরীর কোণে ছিল আমাদের মেটে ঘর, গোয়ালঘর, চাঁপাফুলের উঠোন? কোন ভুক্তি, কোন দন্ড, কোন ভূমি?
বিকেল রঙ বদলাচ্ছে হনহন করে। দাদুর সাথে হাঁটছি ওই মেটে রাস্তায়। পায়ে পায়ে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি শতকের পর শতক। হাজার হাজার বছরের ধুলো জমছে আমাদের পায়ে, জামায়, চুলে। এই রাস্তা দেখেছে বর্গীর দল, কালা পাহাড়। তারও আগে কোনও আদিম কৌম জনগোষ্ঠীর পায়ের ছাপ পড়ে আছে এইখানে, এই ধুলোর আস্তরণে।
প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ বলছেন কায়স্থ, সদগোপ আর কৈবর্ত সমাজ বাঙালীর প্রকৃত প্রতিনিধি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ আর বৃহদ্ধর্মপুরাণ লিখেছে বর্ণসংকর বাঙালির কুল গোত্রের তালিকা। নৃতাত্ত্বিক সেই তালিকা হাতে খুঁজতে বেরিয়েছে বাঙালির জন্মসূত্র, আমার বাপ, দাদা, ঠাকুরদা, তস্য এবং তস্য ঠাকুরদার উৎসমুখের কথা।
ঝুরঝুরে সন্ধ্যা নামছে দীঘির জলে, বুনো ঝোপে, বাঁশের বনে, রাস্তায়। হুন হুনা, হুন হুনা, হুন হুনা রে, হুন হুনা...
পালকি চড়ে নতুন বউ আসছে গাঁয়ে। এসেছিল আমার ঠাকুমা, দিদি ঠাকুমা এবং আরও আরও সমস্ত প্র প্র প্রপিতামহীর দল। নববধূর সাজে, অলক্ত পা ফেলেছিল লালমাটির গায়ে, কাজল টানা চোখ তুলে প্রথম দেখেছিল এ গাঁয়ের গাছপালা, টলটলে দীঘি আর খোড়ো ছাউনির মেটে বসত। নৈষধ চরিতের দময়ন্তী সেদিন নববধূ। লাক্ষারসে রাঙানো ঠোঁট, পায়ে লাল আলতা, কানে মণিকুন্ডল, হাতে কেয়ুর কাঁকন, শঙ্খের বালা। তেমনই কি আমার সেই অজানা কোনও পিতামহীর ছিল– হাতে শঙ্খের বালা, কানে তালপাতার কুন্ডল, পরনে আটপৌরে সুতোর কাপড়, ঘোমটা ঢাকা আয়ত একজোড়া চোখ?
‘দ্য এনালস অফ রুরাল বেঙ্গল’ লিখতে গিয়ে হান্টার আক্ষেপ করেছেন বাঙালির এমন কোনও লিখিত ইতিহাস নেই যা দেখে তার আদিকথা জানা যায়। যা আছে, যেটুকু আছে তা প্রায় সবই রাজাদের দলিল, দানপত্র। সেখানে সাধারণের কথা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কিছু লিপি আছে, সেও সমাজের ছবি নয়। তবুও ইতিহাসবিদ খোঁজে সেইসব অন্ধগলিতে, সেইসব লিপি, দানপত্র, সাহিত্য, পুরাণ কিংবা পোড়ামাটির ফলকে। পাহাড়পুর আর ময়নামতীর বিহারে মন্দিরের গায়ে শিল্পী ঢেলে সাজিয়েছে সমাজের কথা, সাধারণ জীবনের কথা, মাঠেঘাটে কাজ করা মানুষের দিনযাপনের অনাড়ম্বর সব দলিল।
হাওয়া বইছে। বাঁশের পাতায়, তালগাছের মাথায় ঘষা খেয়ে শব্দ হচ্ছে শরশর, শনশন।দীঘির জলে ছোটছোট ঢেউ। মাটির দাওয়ায় বসে কুটনো কুটছে আমার পিতামহী কোনও এক প্রাগৈতিহাসিক সন্ধ্যায়। বেগুন, লাউ, কাঁকরোল, কচু, ইচা, বাচা, শকুল, রোহিতের ঝোলে ঝালে ভাজায় ম ম করছে আমাদের উঠোন, টুপটাপ ঝরে পড়ছে গোলকচাঁপার ফুল। পুকুরঘাটে বর্ষা নেমেছে।
প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোয় তো বটেই; বর্মা, চীন, ইন্দোনেশিয়া, জাপান জুড়ে প্রধান খাবার ভাত মাছ– বাংলা আসাম উড়িষ্যারও তাই। মধ্য ভারত থেকে দক্ষিণে সিংহল অব্দি, পূর্বে উড়িষ্যা বাংলা আসাম পর্যন্ত, সিংহল থেকে অস্ট্রেলিয়া অব্দি ছড়িয়ে ছিল এক আদিম কৌমগোষ্ঠী। নৃতাত্বিকরা বললেন এই সেই আদি অস্ট্রালয়েড জন, যে জনের গঠনগত মিল পাওয়া গেছে কোল মুন্ডা সাঁওতাল শবর হো ভূমিজ উপজাতির শরীরে। করোটি, কপাল, নাক, চোখ, চুল, উচ্চতার খুঁটিনাটি বিচারে জানা গেছে এই আদি অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর সাথে মিশেছে আর এক ভূমধ্যসাগরীয় জনস্রোত আলপাইন, এলপো দিনারীয় স্রোত। এক প্রাগৈতিহাসিক ভোরে মিলেমিশে যাওয়া সেই সংকর স্রোতে জন্ম নিল আমার প্রথম পূর্বজ।
পশ্চিমের গুজরাট থেকে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু হয়ে একটা অ্যালপো দিনারীয় দল পৌঁছেছিল হয়ত উড়িষ্যা, বাংলার মাটিতে। তারও আগে কোনসময় এসেছিল ভূমধ্যসাগরিয় কোন নরগোষ্ঠী। এদের সঙ্গে মিশে গেছিল বাংলার সেইসব আদিম সাঁওতাল, ওঁরাও কিম্বা মুন্ডা জনজাতির আদি অস্ট্রালয়েড রক্ত। রক্তের সাথে রক্তের মিশেলে যেমন জন্ম নেয় নতুন প্রজন্ম তেমনই মিশে যায় রীতিনীতি, আর বিশ্বাস।
জল থৈ থৈ জমি। জল টুপটুপ মেঘ। বীজধান দুলছে হাওয়ায়। তার আগে লাঙল চলেছে, মসৃণ কাদামাটি। সাতপুরুষের জমি, নিজের হাতে লাঙল চষে আমার পূর্বপুরুষ, ফালাফালা মাটি। মাটি ঘাঁটতে ঘাঁটতে আরও আরও বহুদূর হেঁটে যায় আমাদের দাদু,তস্য এবং তস্য বাপ দাদারা। লাঙল নামানোর আগে পুজো দেয় হারান কাকা,পূজো দেয় আমার পূর্বপুরুষ। গোলায় ধান তুলে এনে লক্ষ্মীর বেড় পড়ে মরাইয়ের গায়ে; তেল সিঁদুরের ফোঁটা, গোবর নিকোনো মরাইতলায় অল্পনার আঁকিবুকি। ধানের ছড়া, কলার পাতা, কলা গাছ, হলুদ, পানে আমাদের কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। ভেজা চুল, এলো খোঁপায় আসন সাজায় আমারই কোনও দিদিঠাকুমা।
প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে দ্বীপে জ্বলে ওঠে প্রদীপ। সুপারি, হলুদবাটা, ধানের ছড়া,কলার পাতার গন্ধ মেখে ভেসে যায় শাঁখের আওয়াজ, দূরে বহুদূরে গ্রাম নদী সাগর পেরিয়ে অজানা কোন দেশে। বাঙালির পুজোপার্বনে আদি নর্ডিক আর্য সভ্যতার ছাপ অল্পই, বাঙালির জীবন এবং চরিত্রেও তাই। যেটুকু বা তাও ওপরে, তার গভীরেও সেই আদি অস্ট্রেলিয় ধারা। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলিতে এই পান সুপারি, ধানের ছড়া, কলাপাতা, হলুদের ব্যবহার সমস্ত মাঙ্গলিক কাজে, ধানের ছড়ায় পুজো করে নাগা আর মুন্ডারী জনজাতি। পুজো করে বাঙালি আর তার ব্রাহ্মণ।
সামাজিকভাবে বাঙালি ব্রাহ্মণ উত্তরভারতীয় ব্রাহ্মণের মর্যাদা পায়নি কখনও। বাঙালী ব্রাহ্মণের নিকটতম সম্পর্ক বাংলার কায়স্থ আর বৈদ্যের সাথে। আর বাংলার নমঃশূদ্র চন্ডাল গোষ্ঠীর শরীর গঠনগতভাবে ঘনিষ্ঠ মিল খুঁজে পায় উত্তরের বর্ণব্রাহ্মণের সঙ্গে। ঠিক তারই পাশে বাংলার কায়স্থ কৈবর্ত আর সদগোপ দেহগত বৈশিষ্টে বাঙালির সব বর্ণের সবচেয়ে কাছের জন। বিহারের কিছু গোত্র ছাড়া এই তিন দলের আর কারোর সঙ্গে কোনও মিল তেমন পাওয়া যায়নি, নৃবিজ্ঞানীরা এমনটাই বলেন।
চাষ করে আমার সদগোপ পূর্বপুরুষ। ফালাফালা মাটি, আকাশ ছেঁচা জল, মাটি ঘেঁটে ঘেঁটে ফসল তোলে ঘরে। লাঙলের ফালে তেল সিঁদুরের পূজো অম্বুবাচীর দিনে। লাঙলের ব্যবহার অস্ট্রালয়েড জনের ধারা। লাঙল শব্দও এসেছে এদেরই ভাষা থেকে। অস্ট্রালয়েড ভাষায় লাঙল শব্দের মানে চাষ করা, কিংবা হল। এই একই অর্থে লাঙল শব্দের ব্যবহার সংস্কৃতে। ভাষাতাত্বিক যুক্তি দিলেন যদি কোনও জিনিসের ব্যবহার অজানা হয় তবে তার নির্দেশক শব্দও অভিধানে থাকেনা। আদি নর্ডিক আর্যরা কৃষিকাজ শিখেছে এদেশে এসে, লাঙল শব্দও তখন জুড়ে গেছে সংস্কৃত ভাষার অভিধানে। একই ভাবে দা, করাত, কানি, চোঙা, চিখিল, চোঙ, লেবু, কামরাঙা, ডুমুর ঝোপঝাড় ইত্যাদি এসেছে অস্ট্রিক শব্দ থেকে। দামলিপ্তি(তাম্রলিপ্ত) আর পৌন্ড্র, বঙ্গ এসব শব্দও অস্ট্রিক। নদী পাহাড় জঙ্গলেও পড়ে আছে অস্ট্রালয়েড জনের ছাপ। দাক্ হলো জল, দাক্ থেকে সংস্কৃত উদক। দাম-দাক্ দামোদর। আমাদের ভরা বর্ষার দামোদর।
মেঘ নামছে পাকুড় গাছের মাথায়। রাখাল ফিরে আসছে, দীঘির জলে ডোঙা বেয়ে ঘোরে হারান কাকার ছেলে পরেশ। মাথায় তালের টোকা। পেরিয়ে যাচ্ছি ফণীমনসার ঝোপ, মনসার থান, বর্গী’র মাঠ। বীজধান রোয়ার সময় এখন। চিকচিকে সবুজ ঢেউ ধানি জমির গায়ে। লাঙলের ফালে মাটি কেটে কেটে চাষ করে সেইসব অস্ট্রালয়েড মানুষ, সমতল জুড়ে, ধাপ কেটেকেটে পাহাড়ের গায়ে। চাষ করে আমার চৌদ্দপুরুষ, চাষ করে হারান বাগদী, কানন দুলে, শিবু ডোম।
পণ, গন্ডা, কাহনের হিসেবে বীজ রুইছে। মাড়াই করা খড়ের হিসেব হচ্ছে কাহন দরে। আজ নয়, কাল নয়, হাজার হাজার বছর ধরে আমার চাষী পূর্বজ শিখেছে এই হিসাব। প্রতি চারে এক গন্ডা, কুড়ি গণ্ডায় এক পণ, ষোল পণে এক কাহন। কাহনে পণে আঁটি গুনছে আমাদের ঠাকুরদা। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপের আদিম মানুষ গোনে দু হাতের দশ আঙুল, কুড়ির হিসাবে। গন্ডা হল একক, গন্ডা হল চার। চার কুড়িতে এক পণ। বিড়বিড় করে বীজধানের হিসাব কষে দাদু, বীজতলা জুড়ে সবুজ বিছায় হারান কাকা।
ভুবনেশ্বর শিবের ভাঙ্গা মন্দিরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াই। স্যাঁতস্যাঁতে ভেজা। কবেকার এই মন্দির ছিল জানেনা আমার দাদু, জানেনা গ্রামের কেউ। হয়ত মন্দির নয় ,বৌদ্ধ বিহার। বৌদ্ধ জৈন ব্যবসায়ীরা আসতো দ্বারকেশ্বরের ঘাটে ঘাটে, সওদা হত ধুনো, কাঁসার বাসন, আখের গুড়। ক্রিট দ্বীপের সাথে বাঙালির ব্যবসা ছিল মশলা, হাতির দাঁত, কাপড়ের।
দেবরাজ ইন্দ্র পণিদের কাছে শিখছেন পনীর আর ছানা তৈরির হালহকিকত। পণি থেকে আসা পণ্য কিম্বা বণিক শব্দের সূত্র আমাদের নিয়ে যায় দূরে, ভূমধ্য সাগরের দেশে। এই সেই ভূমধ্যসাগরীয় দল যারা হয়ত এসেছিল তামা'র খোঁজে। প্রফেসর এলিয়ট স্মিথ এই তামার ব্যবহারকেই দায়ী করেছেন মধ্যপ্রাচ্য আর ভূমধ্যসাগর উপকূলের মানুষগুলোর ভারত সহ নানান দেশে ছড়িয়ে পড়ার কারণ হিসেবে, ঠিক যে কারণে মেগালিথ কাল্টে বিশ্বাসী সূর্যপূজারী লোকেরাও ছড়িয়ে যাচ্ছিল পৃথিবীর নানান কোণায়। আর্যভাষী অ্যালপো দিনারীয় দলগুলোও হয়ত এসেছিল এদেরই পিছু পিছু, সম্ভবতঃ নর্ডিক আর্যদেরও আগে।
বর্ধমানের আউস গ্রামের কাছে যে পাণ্ডু রাজার ঢিবি, সেই ঢিবিতেই পাওয়া গেছে ক্রিট দ্বীপে ব্যবহার হওয়া লিপিতে লেখা এক সিলমোহর। মিশরীয় এক নাবিকও তাঁর 'পেরিপ্লাস" বইয়ে লিখছেন প্রায় তিন হাজার বছর আগে ক্রিট দ্বীপে বাঙালি উপনিবেশের কথা।
বর্ষা ছিল সেদিন, উপুড় হয়ে পড়েছে আকাশ। লাল চেলি, চন্দনের টিপ– কড়ি খেলে ঠাকুমা, কড়ি খেলে আমার দিদিঠাকুমা। কড়ি খেলে ফিজি, নিউগিনি, পাপুয়ার মেয়েরা। মাঠঘাট ভাসছে বৃষ্টিফোঁটায়, বৃষ্টি নাচছে দীঘির জলে। কলার ডোঙায় ভেসে বেড়ায় কালু ডোম, পদ্মপাতায় টলটলে জল। পাড়ে ভিজছিল ডোমনি রাধু আর তার বাঁশের চুপড়ি। রাধুর চিকন সবুজ গা, ভ্রমরকালো চোখ, ছড়ানো নাক, ছোট্ট কপাল।
“এক সো পদমা চউসট্ঠী পাখুড়ি।
তহিঁ চড়ি নাচই ডোম্বি বাপুড়ি॥”
ডিঙ্গা ভাসছিল জলে। কাঠের সাথে কাঠ জুড়ে জুড়ে মস্ত ডোঙা ভেসে যাচ্ছিল জলে, প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউয়ের মাথায়। ভেসে যাচ্ছিল আদি অস্ট্রালয়েড মানুষ আর তাদের জলজ অভিসার সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, মেলানেশিয়া ছাড়িয়ে আরও দূরে অস্ট্রেলিয়ার আদিম মাটিতে, প্রাগৈতিহাসিক এক সন্ধ্যার উপকূলে।
বৃষ্টি পড়ছিল খুব… বৃষ্টি পড়ছে জোরে। ভেসে যাচ্ছে মাঠ, দীঘির পাড়। দূর ,অতি দূর থেকে বিনবিন শব্দ উড়ে আসে হাওয়ায় এক কুড়ি, দু কুড়ি... চার কুড়ি পণ…