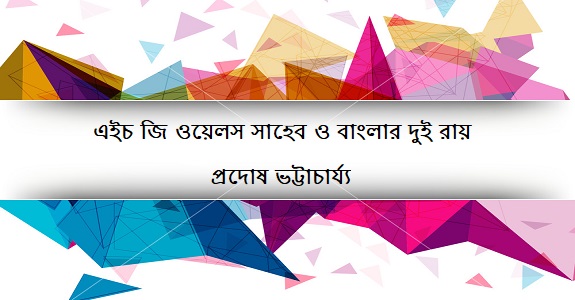৯
ভুখ হরতাল
আমার ভাগ্যে বোধহয় নির্ঝঞ্ঝাটে পড়াশুনো করা নেই। দিনের বেলা পড়তে বসলেই বন্ধুরা বলবে—লেখাপড়া করে যে, গাড়িচাপা পড়ে সে!
আমিও হেসে খাতাপত্তর বালিশের পাশে রেখে ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাই। পড়তে বসি সেই রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর। ঘরের সবাই আলো নেভাতে বললে বারান্দায় গিয়ে একটা ছোট সতরঞ্চি মত বিছিয়ে পড়ায় ডুবে যাই। আমার ইকনমিক্সের বইটার নাম ধনবিজ্ঞান। লেখক ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন লণ্ডন থেকে ধনবিজ্ঞানে বিএসসি অনার্স!
সায়েন্সের বন্ধুরা যতই সাবজেক্টের নাম নিয়ে হাসাহাসি করুক, আমিও ওদের গর্বের সঙ্গে বলি—কিস্যু জানিস না, সাহেবদের দেশে--মানে অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো আর ম্যালথাসের দেশে ইকনমিক্সে সায়েন্সের ডিগ্রি দেয়, এই দেখ।
ওরা ভাল করে দেখে মাথা নাড়ে—দূর! ওটা ছাপার ভুল হবে।
কোন ফচকে ছড়া কাটেঃ
ওহে পোদো গুণধন,
তোমার ধোনের দিকে মন।
এমন সব বিরক্তিকর মেঘলা কুয়াশা ঘেরা দিনে হঠাৎ মহা ক্যাচাল।
সেই ক্লাস এইটের বখা ছেলের দল!
বিকেলে খেলেটেলে তেরোটা কলের কলতলায় (আমাদের লব্জতে ‘তেরো কলের পার্ক’) যখন সবাই হাত-পায়ের কাদা ধুচ্ছিল তখন সুদীপ বলে গোঁফের আভাস দেখা দেওয়া ছেলেটা আমাদের নরমসরম সোমেশ দত্তের ইলাস্টিক দেওয়া খেলার প্যান্ট সবার সামনে একটানে খুলে দেয়।
সোমেশ ওকে এক চড় মারে কিন্তু সুদীপ যথেষ্ট গুণ্ডা। ওকে মাটিতে ফেলে দিয়ে লাথি মারে। সোমেশ কাঁদতে কাঁদতে এসে আমাদের পুরো ঘটনাটা সবিস্তারে বলে। এমনকি নীচু ক্লাসের ক’জন প্রত্যক্ষদর্শীকেও ডেকে আনে যারা তখন সুদীপের মারের ভয়ে বাধা দেয় নি।
আমরা গুরু অমিয়দার দিকে তাকাই।
গুরু হিমশীতল গলায় বলে—সুদীপকে ডেকে আন, বল আমি ডেকেছি।
সুদীপ এসে টের পায় হাওয়া গরম। আমরা সবাই হাজির এবং আমাদের চোখে মুখে হিংস্র ভাব, বদলা চাই!
গুরুর সামনে সোমেশ পুরো ঘটনাটা আদ্যোপান্ত বলে। সুদীপ মিইয়ে যায়।
মিনমিন করে বলে—সোমেশ মিথ্যে কথা বলছে।
--ও, সোমেশ মিথ্যে বলছে আর তুমি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির? লাগা ওকে দুটো থাপ্পড়! সোমেশ, তোকে বলছি।
সোমেশ জড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।
--কীরে, আমরা তো তোকে ওর মতন প্যান্ট খুলে দিতে বলছি না। কিন্তু ও সিনিয়রদের গায়ে হাত তুলেছে! মার দুটো থাপ্পড়।
সোমেশ এগিয়ে গিয়ে নরম নরম হাতে আলতো করে দুটো চড় লাগায়। সে দেখে আমি হেসে ফেলি। এবার গুরুর রাগ চড়ে যায়।
নিজে সুদীপকে ঠাস ঠাস করে দুটো চড় কষায় এবং বলে –এবার যা!
কিন্তু ও চলে যাবার জন্যে পেছন ফিরতেই ওর পাছায় টেনে এক লাথ! সুদীপ ছিটকে বারান্দায় গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে।
ও উঠে দাঁড়ায়, ঠোঁটের কাছে কেট গিয়ে একটু রক্ত বেরিয়েছে।
পরের দিন মেজো মহারাজ গুরু অমিয়দাকে সাসপেন্ড করে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। গুরু কোলকাতা ফিরে গেল। যাবার আগে আমাদের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসল, কিন্তু কিছু বলল না।
এই ঘটনা শ্রীমান পোদোর বুকের ভিতর সঞ্চিত বারুদে কী ভাবে যেন পলিতায় অগ্নিসংযোগের কাজ করে। সে রাত্রের খাওয়াদাওয়ার পরে তাহার গ্রুপের গোপন বৈঠক ডাকে। সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে গুরু শ্রীশ্রী অমিয়দার সাস্পেনশন প্রত্যাহার এবং গুণ্ডা অমিতেশের বিচারের দাবিতে পরের দিন সকাল হইতে ভুখ হরতাল।
সকালে দশম শ্রেণীর কেহ প্রাতরাশ গ্রহণ করিতে গেল না, ড্রিলের মাঠেও নয়। কিন্তু কুড়ি জন ছেলে যখন দ্বিপ্রহরের ভোজনকে অবহেলা করিয়া এবং ক্লাসে না যাইয়া ঘরের বারান্দায় বসিয়া সদ্য রিলীজ হওয়া হিন্দি কমেডি সিনেমা ‘জোহর অ্যান্ড মেহমুদ ইন গোয়া’র হিট সং গাহিতে লাগিল তখন কর্তৃপক্ষের টনক নড়িল।
মহারাজেরা কেহ আসিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের নির্দেশে দুইজন ব্রহ্মচারী, বীরেশদা তাঁহাদের অগ্রগণ্য , অনশনরত আশ্রমবালকদের খবর নিতে আসিলেন, তাঁহাদের পিছনে ক্লাস এইটের ওয়ার্ডেন রণজিৎদা।
--কী হইয়াছে? কেন এরূপ করিতেছ? এমত অভব্য আচরণ কি তোমাদের শোভা পায়? আমাদের আশ্রমের ইতিহাসে কখনও কেহ অশিক্ষিত মজুরের দলের মত অনশন করে নাই।
হাঁসের পালের থেকে প্যাঁকপেঁকিয়ে গলা তুলল ‘আগলি ডাকলিং’ শ্রীমান পোদো।
-- আগে কি কখনও একটা ছেলে অসভ্যতা করলে কিছু না শুনে সিনিয়র ছেলেকে একতরফা সাসপেন্ড করা হয়েছে?
ওরা গোলগোল চোখ করে শুনলেন এবং ফিরে গেলেন।
দু’ঘন্টা পরে শুধু বীরেশদা এলেন।
ওনাকে অভ্যর্থনা করা হল মহম্মদ রফির হিন্দি গান গেয়েঃ
“ দো দিওয়ানে দিলকে, চলে হ্যায় দোনো মিলকে,
চলে হ্যায়, চলে হ্যায়, চলে হ্যায় শ্বশুরাল”।
--আচ্ছা, ভেবে দেখ তোরা না খেয়ে থাকলে আমরা কি খেতে পারি? তোরা কী চাস? কী হলে ওই অনশনটন ভুলে খেতে আসবি? বড় মহারাজ রান্নাঘরের ঠাকুরদের বলে দিয়েছেন—ক্লাস টেনের কোন ছেলে খেতে চাইলে যা চায় সেটা বেড়ে দিতে।
--এসব কায়দা করে কিছু লাভ হবে না বীরেশদা। আগে আপনারা অমিয়দার সাসপেনশন তুলে নিন। আমরাও অনশন তুলে নেব। তারপর সুদীপ এবং সোমেশকে এবং যারা তখন ঘটনাটা দেখেছে তাদের ডেকে সব শুনে আপনারা বিচার করুন। তখন যা বলবেন মেনে নেব।
--শোন, বড় মহারাজ কথা দিয়েছেন যে তোদের দুটো দাবিই মেনে নেওয়া হবে। আগে খেয়ে নে। তারপর তোদের আলোচনায় ডাকবেন।
--কাকে কথা দিয়েছেন? আমাদের অফিসে ডেকে সবার সামনে উনি কথা দিন আর অমিয়দার সাসপেনশন তুলে নিয়ে ওর বাবাকে ফোন করে বলুন –কাল ওকে আশ্রমে পৌঁছে দিতে, ব্যস।
--তোরা আমাদের অবিশ্বাস করছিস?
--কাউকেই অবিশ্বাস করছি না তো। কিন্তু আমাদের শর্ত আপনাকে জানিয়ে দিলাম। গিয়ে বড় মহারাজকে বলুন।
ওরা ফিরে যান, কিন্তু আমাদের ভুখ হরতালের খবরটা স্কুলের ছেলেদের মাধ্যমে সমস্ত টিচারদের কাছে, মায় যে টিচাররা আশ্রমবাসী তাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ ‘সমর্থন’ আসতে থাকে। হোস্টেলের টিচাররা গোপনে আমাদের দু’জন প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে “পূর্ণ সমর্থন” জানিয়ে বলেন ভয় না পেতে। আরও বলেন যে চুপিচুপি খেতে চাইলে ওঁরা খাবার আনিয়ে দেবেন।
অনশনরত বালকের দল খুব খুশি। কিন্তু এবার অনশনের নেতৃত্ব কেমন করে যেন প্রদ্যুম্ন ওরফে পোদোর ঘাড়ে চেপেছে। ব্যস, পোদো বার খেয়ে ক্ষুদিরাম হয়ে গেল।
ও গম্ভীর মুখ করে গুরুর অনুকরণে দু’বার গলা খাঁকারি দিয়ে গলার আওয়াজ মোটা করে বলল—“ ব্রহ্মিষ্ঠের চরণে প্রণিপাত। আমার মাত্র গোধনে প্রয়োজন ছিল”।
এ আবার কী!
--এটা জনকসভায় যাজ্ঞবল্ক্যের ডায়লগ। জনক বললেন -যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি এই সোনার পাতে শিং মোড়া একহাজার গাভী নিয়ে যান। তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর এক শিষ্যকে আদেশ করলেন – যা রে! ওই গরুগুলোকে পাঁচন বাড়ি লাগিয়ে আমার আশ্রমে নিয়ে যা।
তখন এক ঋষি কুপিত হয়ে বললেন—তিষ্ঠ! যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি নিজেকে ব্রহ্মজ্ঞ মনে কর নাকি? বলি কবে থেকে?
তখন জবাবে উনি ওপরের ডায়লগ ঝেড়েছিলেন। তারপর কী হইয়াছিল জানে শ্যামলাল। একে একে সবাই, মায় গার্গী বলে এক মহিলা বিদুষী সবাই যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে হার মানলেন।
--এসব কোথায় লেকা আচে?
--বৃহপদারণ্যক উপনিষদে।
--তুই উপনিষদ পড়েছিস? শালা পোদো, খাবার সময় গীতাপাঠের পারমিশন পেয়েছিলি বলে উপনিষদ নিয়ে ফালতু গুল মারবি? যত্ত আলফাল ফাণ্ডা।
এবার বিপ্লব মুখ খোলে।
--এর জন্যে মূল উপনিষদ পড়ার দরকার হয় না। এটা ক্লাস নাইনের ধর্মক্লাসের যে বইটা ছিল—“উপনিষদের নির্বাচিত গল্প”, তাতেই আছে।
আমি অবাক। বিপ্লব আমার সাপোর্টে মুখ খুলেছে! ও কি আশা করে আমাদের সম্পর্ক ফের আগের মত হয়ে যাবে?
কিন্তু খেঁকিয়ে উঠেছে প্রশান্ত—এঃ , শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল! শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর। আব্বে, কোন শাস্তরে কী লেখা আছে জেনে আমাদের এখন কী লাভ? কাজের কথা বল। স্যারেরা বলছেন লুকিয়ে খেয়ে নিতে, ওঁরা খাবার সাপ্লাইয়ের দায়িত্ব নিচ্ছেন। দু’দিন ধরে না খেয়ে আছি। আমি বাবা, স্যারের কথা মেনে চলার পক্ষে, পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে।
তোরা কী বলিস?
রমেন বলে—আগে পোদোর কথা শোনা যাক। এখন ওই লীডার। পেট খারাপের ব্যামো আর বিচ্ছিরি পাদে, কিন্তু ওই লীডার।
সবাই আমার দিকে তাকিয়ে।
আমি প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাই, এক এক করে।
--শোন, স্যারেরা সমর্থন দিচ্ছেন , ভাল কথা। এর মানে বড় ও মেজো মহারাজের তুঘলকি ব্যবহারে ওনারা অসন্তুষ্ট, ক্ষুব্দ। হয়ত ওনাদেরও কোন পুরনো ইস্যু রয়েছে, যা আমরা জানি না। কিন্তু আমাদের জোর হল নৈতিকতা। আমরা যদি লুকিয়ে খাবার খাই, তাহলে স্বামীজিরা ঠিক জেনে যাবেন। কে জানে, স্যারেরদের মধ্যেই কেউ মহারাজের স্পাই কি না!
আমাদের নিজেদের লক্ষ্য ভুলে গেলে চলবে না। যতক্ষণ আমাদের গুরু অমিয়দার সাসপেনশন বহাল রয়েছে ততক্ষণ আমরা খাবার খাব না, ব্যস।
সুদীপের বিচার ও শাস্তি এজেন্ডার দু’নম্বর। ওটা নেগোশিয়েবল। কিন্তু অমিয়দা আগে ফিরে আসুক। তারপর ওই লীডার হবে, আমার কাজ শেষ।
যাজ্ঞবল্ক্যের গল্পটা রেলিভ্যান্ট। আমাদের নিজেদের লক্ষ্যের ব্যাপারে ক্লিয়ার থাকতে হবে।
কিন্তু আমি কোন ডিক্টেটর নই। সবাই মিলে যেটা ঠিক হবে, সেটাই মেনে চলব।
সবাই চুপ।
প্রশান্ত মুখ খুলল।
--নাঃ পোদো শালা ঠিক বলেছে, এক্কেবারে লীডারের মত। হ্যাঁরে পোদো, তুই কি বড় হয়ে ইলেকশনে দাঁড়াবি?
রমেন হেসে ফেলে।
--ভাগ শালা, ও কোন দুঃখে ওসব হবে। ও হবে কোন একটা আলাদা মিশনের মহারাজ। খুব গীতা-উপনিষদের ফাণ্ডা ঝাড়ে না? ঘাবড়াস না পোদো, এই বাংলা বাজারে দশটা-পাঁচটা চাকরি করার চেয়ে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসি হবি--দু’বেলা খাবারের চিন্তা থাকবে না।
--হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাত-কাপড়-বিছানা সব গ্যারান্টি। কত লোক তোকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে। তুই আশীর্বাদ দিবি। তোর আশীর্বাদে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া মিটে যাবে। যার বিয়ের দশ বছর পরেও কোলে বাচ্চা আসে নি, তোর আশীর্বাদে সব হবে।
বিয়ে করে সংসার করতে গেলে কত ঝামেলা। বছর বছর চ্যাঁ-ভ্যাঁ, পুজোর শাড়ি , বাচ্চাদের বাবা স্যুট। গয়না গড়িয়ে দাও, পুরীতে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে নিয়ে যাও। কত বায়নাক্কা ! তার চেয়ে সন্ন্যাসী হওয়া ভাল।
হো-হো-হা-হা-হি- হি!
এবার রমেন গান ধরে—জানেওয়ালে জরা হোঁশিয়ার, ইহাঁকে হম হ্যায় রাজকুমার।
এরপর সমবেত কণ্ঠে –লাল ছড়ি, ময়দান খড়ি, ক্যা খুব লড়ি, ক্যা খুব লড়ি।
কেউ কেউ শাম্মী কাপুরের ব্যর্থ অনুকরণ করে। আমরা সবাই নাচতে থাকি।
কেউ খেয়াল করি নি যে অনেকক্ষণ ধরে বৃহস্পতি দাস একপাশে দাঁড়িয়ে আমাদের বাঁদর নাচ দেখছে, এবং কিছু বলছে।
প্রায় ছ’ফিট লম্বা কুচকুচে কালো বৃহস্পতি আমাদের আশ্রমের জমাদার। নালা-নর্দমা সাফ করে। কিন্তু ওর পরনে্র স্যাণ্ডো গেঞ্জি এবং হাফপ্যান্ট ধবধবে সাদা। এসেছে বিহার থেকে, ভাঙা ভাঙা বাংলা বলে। ওর ঘরে গিয়ে দেখেছি বিছানার চাদর তেমনই পরিষ্কার।
আমাদের বলেছিল যে ওদের গাঁয়ে ওরা অছুত, অস্পৃশ্য; তাই গাঁয়ের সীমানার বাইরে ধাঙড় বস্তিতে ওদের ঘর।
ওসব নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য, উনি জাতপাত ছোয়াছুঁয়ি এসবের থোড়াই কেয়ার করতেন। ঠাকুর নিজে ব্রাহ্মণ হয়ে ধনী কামারনীর রাঁধা ডাল খেতেন তো।
এর ফলে এমন দোস্তি হল যে একদিন ওয়ার্ডেন রণজিৎদা ক্লাস কামাই করা রমেনকে খুঁজতে খুঁজতে আবিষ্কার করলেন মেথর বৃহস্পতির বিছানায়। গাঢ় ঘুমে তলিয়ে আছে রমেন।ভর দুপুরে কপালে মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম, আর হাতে একটা জ্বলন্ত সিগ্রেট, তখনও ছ্যাঁকা লাগে নি।
রণজিৎদা জানতে পারেন নি যে ওনার বিছানায় গুরুর ফেলা অ্যাসিডটা ছিল পায়খানা পরিষ্কার করার সালফিউরিক। প্রশান্ত বৃহস্পতির ঘর থেকেই জোগাড় করেছিল।
সে যাক গে, এখন বৃহস্পতি কিছু একটা বলার জন্যে হাঁসফাঁস করছে, আমাদের ইশারা করছে নাচ থামাতে।
ও বলল যে বড় মহারাজ অনশন করা সব ছাত্রের গার্জেনদের তলব করেছেন। যাদের বাড়ি বাঁকুড়া, পুরুলিয়া বা বর্ধমানে তাদের ট্রাংককলে খবর দিয়েছেন। আর দূরের লোকজনকে টেলিগ্রাম করেছেন।
দু’জন গার্জেন এরমধ্যেই এসে অফিসে বসে আছেন। বিশুর ও অনিন্দ্যের বাবা। বৃহস্পতিকে বড় মহারাজ আদেশ করেছেন ওই দু’জনকে ডেকে অফিসে নিয়ে যেতে।
সবাই আমার দিকে তাকায়। আমি নিরুত্তর। এই চালের কাটান কিসে সেই মন্তর আমার জানা নেই। সেই মুহুর্তে বুঝে যাই যে আমি লীডার নই। আমার মধ্যে সেই মেটেরিয়াল নেই। আবেগের মাথায় চলি—গ্যাস বেলুনের মতো।
হ্যাঁ, গুরুর মধ্যে ছিল। কিন্তু ও তো ময়দানে নেই। অতঃ কিম্?
অপেক্ষা করে দেখতে হবে কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।
বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না।
ফিরে এল বিশু ও অনিন্দ্য, চোখের জল মুছতে মুছতে।
একটু একটু করে যা বলল তাতে বুঝলাম মহারাজ গার্জেনদের ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছেন। আসল ঘটনা না বলে জানিয়েছেন যে ক্লাস টেনে এসব করলে বাচ্চাদের পরকাল তো গেছেই ইহকালও ঝরঝরে।
মিশন থেকে রাস্টিকেট হলে কোথাও অ্যাডমিশন হবে না। ক্যারিয়ার মায়ের ভোগে গেল!
ওরা আসল ঘটনার কথা বলতে যেতেই গার্জেনরা এক ধমকে থামিয়ে দিয়েছেন। স্বামীজির কাছে পা’ ধরে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছেন। মহারাজ ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে ক্ষমা করে দিয়েছেন। বাবারা লিখে দিয়েছেন যে ওনাদের বাচ্চা আর এমন অবাধ্যতা করবে না।
ওরা ফিরে আসার আগে মেজো মহারাজ উঁচু আওয়াজে বললেন –আপনার বাচ্চা নিষ্পাপ। কিন্তু তিনটে ছেলে এখানকার আবহাওয়া দুষিত করছে—অমিয়, প্রদ্যুম্ন আর প্রশান্ত।
পালের গোদাকে আমরা সাসপেন্ড করেছি, তাই পরের জন সবাইকে উস্কানি দিচ্ছে। ছেলেকে বলুন প্রদ্যুম্নের সঙ্গে না মিশতে।
দুটো কথা বুঝতে পারলাম।
এক, আমার বাড়িতেও টেলিগ্রাম গেছে। তিনচার দিনের মধ্যে আমার বাবাও এসে পড়ল বলে। আমার বাবা এক্স-মিলিটারি ম্যান, আমার জন্মের আগে ১৯৪৮ সালে কাশ্মীরের যুদ্ধে লড়েছিল। এখন ভিলাই স্টিল প্ল্যাণ্টের ইঞ্জিনিয়ার বটে, কিন্তু মেজাজ সেই মিলিটারি মার্কা। আমার দুই কাকা আড়ালে ওনার নাম দিয়েছে –তারাস বুলবা, গোগোলের রাশিয়ান বইয়ের কসাক জেনারেল।
টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটি নিয়ে এলে কী হবে ভেবেই আমার জ্বর আসার জোগাড়।
দুই, আমার আশ্রমবাস উঠল বলে!
হ্যাঁ, বলা বাহুল্য ভুখ হরতাল দ্বিতীয় দিনেই ভেঙে গেছল। সবার বাবা এসে ছেলেদের আচ্ছা করে কড়কে দিলেন। কেউ কেউ তো মারতেই উঠেছিলেন। একজন বললেন—তোরা ছাত্র, না কারখানার মজুর? ভেবে বল্।
আর আমাদের গুরু অমিয়দার সাসপেনশন উঠে গেল। ও ফিরে এল মনমরা হয়ে। কিন্তু আমাদের ঘরে ঢুকেই আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমাদের গুরুর চোখে জল দেখলাম, প্রথমবার।
রাত্তিরে গুরুকে চুপি চুপি বললাম- বুদ্ধি দাও। বাবা এলে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ঠ্যাঙাবে, হয়ত ছাড়িয়ে নিয়ে আরও কড়া শাসনের কোন হস্টেলে ভর্তি করে দেবে। কী করি?
--রাত্তিরে খেয়ে দেয়ে ভাল করে ঘুমো। দু’দিন খাসনি, শুধু আমার জন্যে? আমার সম্মানের জন্যে!
কাল সকালে একটা রাস্তা বের করব।
পরের দিন সকাল। রোববার। জলখাবার খাওয়া হয়ে গেছে। আমার আর তর সইছে না।
--শোন, পোদো। তুই আমাকে একবার মুজতবা আলীর লেখা থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে পড়াশুনো ছেড়ে দেওয়া, তারপর শান্তিনিকেতনে ভর্তি হওয়ার গল্প শুনিয়েছিলি না?
--হ্যাঁ, কিন্তু সে তো -----
গুরু আমাকে হাত তুলে থামায়। বলে সেই সময় উনি মজা করে একটা কমেন্ট করেছিলেন না?
--হ্যাঁ, খেটেখুটে পরীক্ষা পাশ করার চেয়ে পরীক্ষা না দেওয়ার সম্মান বড় হয়ে গেল বা ওইরকম কিছু একটা।
--জাস্ট দ্য থিং! তোকেও তাই করতে হবে।
--মানে?
--ডিফেন্স নয় অফেন্স। তোর নামে কমপ্লেন হওয়ার আগেই তুই তারাস বুলবার কাছে, থুড়ি মেশোমশায়ের কাছে কমপ্লেইন করে দে।
ফিসফিস ফিসফিস ফিসফিস!
গুরু আশুতোষ দেবের বেঙ্গলি টু ইংলিশ ডিকশনারি খুলে বসেছে।
অতঃপর গুরু কর্তৃক আদেশিত হইয়া আশ্রমবালক শ্রীপ্রদ্যুম্ন তাহার পিতৃদেবকে ইনল্যান্ড লেটারে নিম্নরূপ পত্র পাঠাইলঃ
“বাবা, আমি আশ্রমে থাকতে চাই না। এখানে খুব “হোমোসেক্সুয়ালিটি” হয়”।
(চলবে)