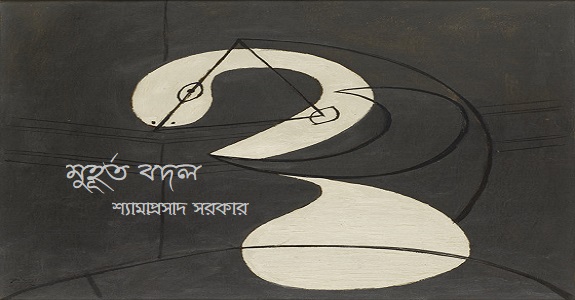৫
সেই ঐতিহাসিক এডিটোরিয়াল বোর্ডের মিটিং আমাদের ঘরেই হয়েছিল। তাতে তিনজন বোর্ড মেম্বার ছাড়া অন্য বন্ধুরাও ছিল।
সবাই আমাকে খ্যাপাতে লাগল।
বলল আমি ওই অত্যাধুনিক কালজয়ী কবিতাটি ছাপিয়ে একটা শোরগোল তুলে দিতে পারতাম। তার বদলে বোকামি করে অমর হবার সুযোগ হেলায় হারালাম।
--দেখ, গুরু। তুমিও ভাল করেই জান যে কবিতা-টবিতা নয়, ওটা একটা অশ্লীল ছড়া -- যেটা নিয়ে শুধু হ্যা-হ্যা করে হাসা যায়, যেমন বিপ্লব হেসেছিল। কিন্তু ছাপানো?
-- অশ্লীল কেন? কোন অশ্লীল শব্দ তো হেডস্যারও খুঁজে পান নি।
গুরু গম্ভীর, কিন্তু চোখে দুষ্টুমি।
--আরে হেডস্যারের কথা ছাড়। তুমি ভাল করেই জান যে এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে একটা শরীরের ব্যাপার নিয়ে ছ্যাবলা ইয়ার্কি আছে।
প্রশান্ত ফিচেল হেসে বলল-- রবি ঠাকুর, বুদ্ধদেব বসু -এঁদের কবিতায় ও কত শরীরের বর্ণনা আছে, তাতে কবিতা অশ্লীল হয়ে গেল। তোর ভাটপাড়ার টুলো পন্ডিত হওয়া উচিত পোদো।
-- ফালতু কথা বলবি না তো! তুই কবিতার কি বুঝিস? রবি ঠাকুরের কবিতায় শরীর?
এবার বিপ্লব ফিকফিকিয়ে হাসে।
-- হল না পোদো। রাগের চোটে যুক্তি হারাচ্ছিস।
রবিঠাকুর লেখেন নি-- নিরাবরণ বক্ষে তব নিরাভরণ দেহে?
বুদ্ধদেব তো আরও এককাঠি এগিয়ে-- বক্ষ তব ঢাকিয়া দিনু চুম্বনেরই চাপে! ভাব তো-- এর চেয়ে নরেশের ওই " টালিগঞ্জ -বালিগঞ্জ" বেশি অশ্লীল কি? হেডস্যার তো ধরতেই পারেন নি।
আমি মরিয়া হয়ে বলি--ওটা কোন কবিতা হল? টিফিনেতে খেতে দেয় পাঁউরুটি কলা-- এতে অন্ত্যমিল -ছন্দ - একটা তির্যক প্রতিবাদ এসব রয়েছে। নরেশের ওটায় বখামি ছাড়া আর কি আছে? কয়েকটা স্টেশনের নাম লিখলে সেটা কবিতা হয় কি করে?
বিপ্লব আবার দাঁত বের করে।
-- শুধু স্টেশনের নাম? ওই বজবজ-বজবজের দ্বিত্ব একটি রেলওয়ে টাইমটেবিলের পাতাকে কাব্যিক সুষমায় মন্ডিত করিয়াছে। একেবারে অনেক- কথা- যাও যে বলে -কোন কথা না বলি--হয়েছে।
সবাই টেবিল চাপড়ে হেসে ওঠে। আমি রেগে মেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করছি , ক্লাস সেভেনের কিশোর দৌড়তে দৌড়তে ঢুকে হাঁপাতে থাকে।
-- আরে অমিয়দা, বিপ্লবদা! আপনারা সব্বাই চলুন। শীগ্গির শীগ্গির! আমাদের বিজিত স্যার আবার পরীক্ষায় ফেল করেছেন। উনি কাঁদতে কাঁদতে খেলার মাঠের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। কিছু একটা হয়ে যেতে পারে।
আমরা ঝগড়া ভুলে ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড় লাগাই। ঘরে তালা দেওয়ার কথা কারও মনে নেই।
বিজিতদা আমদের আশ্রমের একটি চরিত্র যাকে সবাই ভালবাসে। এই ভালবাসার সঙ্গে কোথায় একটু করুণা মেশানো, কারণ ওঁর ডান পায়ের পাতা দোমড়ানো মোড়ানো; বেঁটে খাটো মানুষটি চলেন দুলে দুলে। পড়ান প্রাইমারি স্কুলে। আশ্রমে পেটভাতায় থাকেন আর রাত্তিরে ক্লাস সিক্স ও সেভেনের আশ্রমিক বাচ্চাদের ইংরেজি টেক্সট ও ট্রান্সলেশন পড়ান।
ওঁর সঙ্গে পরিচয় হলে মনে হয় ছোটবাচ্চাদের ভাল করে পড়ানো ছাড়া ওঁর জীবনে কোন উদ্দেশ্য নেই। বিয়ে করেন নি। একটি সাদা হাফ শার্ট , ধুতি ও হাওয়াই চপ্পল--ব্যস্। একজন মানুষের আর কি চাই!
ওঁর ভক্ত সংখ্যা অনেক। অনাবিল হাসি, একেবারে শিশুর মত। আর উনি খুব ভাল ভূতের গল্প বলতে পারেন। বলর ভঙ্গীতে ও মুখে নানারকম শব্দ করে উনি পরিবেশ এমন করে দেন যে নাইনে পড়ার সময়ও আমরা একে অন্যের গা ঘেঁষে বসতাম।
আমাদের উনি পড়াতেন না, কিন্তু বিজিতদা কবে গল্প বলবেন বললেই একটু ভেবে বলতেন শুক্রবার সন্ধ্যেয়। আমরা নিজেদের পড়াশুনো ছেড়ে ওঁর ক্লাসে ভিড় করতাম। সুনীল মহারাজ দেখেও দেখতেন না।
সবচেয়ে বিখ্যাত গল্প হল-- যুদ্ধের সময় ছিটকে পরা এক বন্ধু স্ট্যানলি না ব্রিয়ারলি, অন্য ছোটবেলার বন্ধুর থেকে ইয়র্কশায়ারে গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে দেখা করার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি পেল।
তারপর কি হইল সবাই জানে।
পরে আমাকে এক স্যার বলেছিলেন ওটা ওঁদের ম্যাট্রিকের কোর্সে একটি ইংরেজি কবিতার ন্যারেশন।
কিন্তু এই সর্বজনপ্রিয় বিজিতদাও একেক্দিন খেপে উঠতেন। ওঁর টিউটোরিয়ালের বেয়াড়া বাচ্চাদের ভালবেসে বুঝিয়ে সুজিয়ে যেদিন পোষ মানাতেন পারতেন না , সেদিন খুব হতাশ হয়ে খানিকক্ষণ মাথা নীচু করে মাটিতে পাতা সতরঞ্চির উপর বসে থাকতেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নিজের গালে চড় মারতেন -- মুখে আওয়াজ করতেন 'ত্যাট্ ত্যাট্!'
দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলতেন--আমি এক ক্যালানে মাস্টার, সারাজীবন ধরে দাঁতকেলিয়ে যাব।
ছেলের দল হেসে কুটিপাটি।
এরপর খোঁড়া পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এক খাট থেকে অন্য খাটে বাঁদরের সর্দারগুলোকে তাড়া করে বেড়াতেন। কেউ ভয় পেত না, উনি কাউকে জোরে মারতে পারতেন না, নিজেকেই শাস্তি দিতেন।
অন্য ক্লাসের ছেলেরা এসে তামাশা দেখত। তারপর বড়রা বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করত। তখন ওঁর চোখে জল। বাঁদর ছাত্রগুলোকে জড়িয়ে ধরতেন।
এ হেন সুনীলদা কিছুতেই আর ম্যাট্রিকের বেড়া ডিঙোতে পারলেন না।আমাদের চোখের সামনে বার তিনেক প্রাইভেটে পরীক্ষা দিলেন-- প্রত্যেকবার একই ফল, অন্ততঃ দুই বিষয়ে ফেল। একটা অবশ্যই অংক।
পরীক্ষার দুদিন আগে থেকে ছুটি নিতেন , একবেলা উপোস করে হলে যেতেন, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতেন। আমরা জেনেছিলাম --পাস করলে মিডল সেকশনে পড়াতে পারবেন, মাইনে বাড়বে।
এত ভাল পড়াতেন , ফেল কেন হচ্ছেন --এ এক রহস্য। আমরা এটাকে ভগবানের অবিচার মনে করতাম। পরীক্ষার ফল বেরোনোর আগে আমরাও ওঁর জন্যে প্রার্থনা করতাম--ঠাকুর, অনেক পরীক্ষা নিয়েছ, এবার তো পাশ করিয়ে দাও। পাঁচ সিকে মানত করছি।
স্যারকে বলেছিলাম--কোন চিন্তা করবেন না। আমরা সবাই আপনার জন্যে প্রেয়ার করেছি। এবার কেউ ঠেকাতে পারবে না।
কোথায় বিজিতদা?
ওই যে বেঁটে মত ধুতি পরা লোকটি খোঁড়াতে খোঁড়াতে দ্রুত পায়ে প্রেয়ার হলের দিকে যাচ্ছে।
আমাদের আগেই উনি পৌঁছে গেছেন হলে।
আমরা ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। কেউ কেউ বারান্দায় থেমে গিয়ে জানলা দিয়ে দেখতে লাগলাম।
প্রায়ান্ধ জনহীন হল। শুধু ঠাকুর-মা-স্বামীজির ছবির সামনে পিলসূজের উপর পেতলের প্রদীপের শিখা। সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন বিজিত স্যার--আমাদের বিজিতদা। চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে দুই গাল। কেঁপে কেঁপে উঠছে ঠোঁট। অস্ফুট স্বরে শোনা যাচ্ছে বুকভাঙা হাহাকার-- ঠাকুর, এ কী করলে তুমি, ঠাকুর!
এই বিংশশতাব্দীর আশ্রমের গল্প যেন ক্যান্টারবেরি টেলস্ । কত বিচিত্র জলছবির সমাহার। কত বর্ণাঢ্য চরিত্র। যেমন ছাত্রপ্রাণ খঞ্জ বিজিতদা, তেমনি একজন হলেন অন্ধ পাখোয়াজ বাদক নগেশদা।
শুধু শারীরিক পঙ্গুত্বে নয়, এঁদের দুজনের আসল মিল কাজের প্রতি সমর্পণে, নিজেকে উজাড় করে দেওয়ায়। আমার বালকবুদ্ধির মাপকঠিতে আশ্রমের ভাল কিছু জিনিসের মধ্যে এই দুজন প্রায় নায়কের স্থানে বসে আছেন।
প্রতিদিন সন্ধ্যেয় আরাত্রিক 'খন্ডন ভব বন্ধন' শুরু হওয়ার আগে দেখা যেত উনি কারও হাত ধরে বা একাই হাতড়ে হাতড়ে মাপা পা ফেলে প্রেয়ার হলে ঢুকছেন। পোদো ওর কাছে গিয়ে বসে একটা বড় আটার ভিজে তাল নিয়ে ওনার নির্দেশমত পাখোয়াজের বাঁয়ার দিকটায় চেপে চেপে বসিয়ে দিত।
অতি বিলম্বিত লয়ে চৌতালে শুরু হত আরাত্রিক। বলিষ্ঠ হাতের চাপড়ে বাজত চৌতালের ঠেকা। খঞ্জনি হাতে পোদো মেলাতে গিয়ে ঘেমে যেত। তারপর দুনি চালে রিপিট হত। পোদো ওনার হাতে দেখানো মাত্রা ও ইশারায় চারপাশের বন্ধুদের সামনে ঘ্যাম নিয়ে খঞ্জনি বাজাতো।
যেই না শেষের চার লাইনে 'নমো নমো প্রভু বাক্যগুণাতীত' আর 'ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ'--- ত্রিতালে ও একতালে জলদ বাজত, নগেশদার পাখোয়াজও গুরু গুরু মেঘগর্জনের মত কথা বলে উঠত। শেষে তেহাই -টেহাই দিয়ে সমে এসে নগেশদা কাঁধের গামছা দিয়ে ঘাম মুছতেন। পোদোর বুকের মধ্যে ঝরণা কল কল বইত আর ও প্রেয়ার ভুলে গিয়ে একটা বড় সড় পেতলের খঞ্জনি নিয়ে পাখোয়াজের বাঁয়ার দিক থেকে সেই ভিজে আটার শুকিয়ে যাওয়া দলাটিকে ঘষে ঘষে তুলত যতক্ষণ না নগেশদা হাত বুলিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বলতেন --ঠিক আছে।
কালীপূজার রাত। চারদিকে তুবড়ি, ফুলঝুরি হাউয়ের সমারোহ। দোদুমা ও চকলেট বোমের কানফাটানো আওয়াজ।
জন্মবুড়ো পোদোর এর চেয়ে মন টানে প্রেয়ার হলের বারান্দায় জাজিম পেতে সারারাত্তির কালীকীর্তনের জমাটি আসর। কত খেয়ালিয়া ধ্রুপদীয়া এসেছেন। তবলা ও পাখোয়াজে সেই আদি ও অকৃত্রিম নগেশদা। আজ উনি একটা ধোপদুরস্ত শাদা শার্ট পড়েছেন, ধুতিও নীল লাগিয়ে কাচা। শীতের হালকা আমেজ, তাই গায়ে একটি চারটাকার মেটে রঙের মলিদা। আর আজকে খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ির জায়গায় পরিপাটি করে কামানো গাল।
এসেছেন সুদূর হরিনাভি থেকে ধ্রুপদীয়া সংগীতাচার্য অমরনাথ ভট্টাচার্য। ধপধপে ফর্সা, টাক মাথা, চোখে ছানি, বয়েস সত্তর পেরিয়ে আশি ছোঁয় ছোঁয়। গায়ে গরদের পাঞ্জাবি ও মুখে এক অভিজাত গাম্ভীর্য।
যে কেউ গান গাইবে বলছে সে নগেশদার কানের কাছে ফিসফিস করছে আর উনি উঁচু আওয়াজে বলছেন--গুরুদেব , এবার বিশ্বনাথ একটি হামীর ( বা জয়জয়ন্তী) গাইতে চায়, আপনি অনুমতি দিন। উনি মাথা নাড়লে সে নবীন গায়ক তাঁর হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম করে তানপুরা পিড়িং পিড়িং সেরে গান ধরছে।
এর পর অমরনাথ নিজে গাইতে লাগলেন। আগের মত দম নেই , লম্বা তান করতে পারছেন না, তবু সুর লাগানো দেখে ভক্তেরা আহা আহা করে উঠছে।
এদিকে পুজো শেষ, রাত ফুরিয়ে এল। এবার শান্তিজল নেবার পালা। যজ্ঞের আগুন কখন নিভে গেছে।
সবাই উঠি উঠি করছে; নগেশদা বললেন--গুরুদেব একটি ঝাঁপতাল গেয়ে শেষ করলেন। অমরনাথ ধরলেন ভৈরবীতে ঝাঁপতাল-- ভবানী দয়ানী, মহাবাক্যবাণী।
গান শেষ হল। কারও মুখে কথা নেই। নগেশদার অক্ষিগোলকহীন কোটর থেকে জল গড়াচ্ছে।
একজন নতুন ওয়ার্ডেন এসেছেন—রণজিৎ দত্ত। উনি বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে ইকনমিক্সে অনার্স পাশ করে বর্ধমান ইউনিভার্সিটির ইকনমিক্স বিল্ডিংয়ে এম এ'র ক্লাস করছেন। বছরখানেক আগে ওঁর বাবা মারা গেছেন। পড়াশুনোর খরচা উনি স্টাইপেন্ড থেকে সামলে নিচ্ছেন। কিন্তু থাকা খাওয়ার খরচা?
ব্যব্স্থা হল যে উনি আমাদের ওয়ার্ডেন হওয়ার শর্তে আশ্রমে পেটভাতায় থাকবেন, দিনের বেলায় ট্রেনে করে বর্ধমান ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ক্লাস করে বিকেল নাগাদ ফিরে আসবেন। ওঁর দায়িত্ব রাত্তিরে বড় ছেলেদের সামলে সুমলে ডিসিপ্লিনের মধ্যে রাখা এবং দরকারমত পড়াশুনোয় গাইড করা।
উনি অন্য ওয়ার্ডেনদের মত ধুতি পড়তেন না। আসমানি নীল রঙের স্লিপিং স্যুট পরে থাকতেন। আশ্রমের মধ্যে সেটা প্রায় ফ্যাশন শোয়ের মর্যাদা লাভ করল।
লম্বা ফর্সা চোপসানো গাল ও গর্তে বসা চোখের রণজিৎদার মুখে সারাক্ষণ একটি অনাবিল হাসি লেগে থাকত। উনি আমাদের পড়াতেন না, টেবিল টেনিস খেলতে শেখাতেন। গল্প বলতেন--নানারকমের গল্প। ইউনিভার্সিটির ক্লাসে বন্ধুদের হয়ে প্রক্সি দেওয়া ডাকসাইটে মেয়েদের গল্প। এবং অবশ্যই কিছু যৌনগন্ধী গল্প ও জোকস্।
আস্তে আস্তে উনি আমাদের বন্ধু হয়ে গেলেন।
একদিন ক্লাস সেভেনের একটা নতুন ভর্তি হওয়া বাঁদর ছেলে ওনাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ছড়া শোনালঃ
খ্যাঁচাদাদা যায়,
নীল পাজামা গায়,
বড় বড় মেয়েরা কেউ ফিরে না তাকায়,
খ্যাঁচা ফিরে ফিরে চায়।
উনি আমাদের ঘটনাটা বলেন নি। কিন্তু আমরা ছেলেটাকে ডেকে এনে ভাল করে চাঁটালাম। পরে রণজিৎদা যখন ছেলেটার ঘরে রাত্তিরে দরজা কেন বন্ধ নয় দেখে ঠেলে ঢুকতে গেলেন , অন্ধকারে ৪৫ ডিগ্রিতে ভেজিয়ে রাখা দরজাটার মাথায় রাখা এনসিসির বুট ও একটা মুড়ো ঝাঁটা ওঁর মাথায় পড়ল। চিৎকার চেঁচামেচির পরে আলো জ্বললে দেখা গেল ঝাঁটার মধ্যে গুঁজে রাখা একটা কালির দোয়াতও মুখ খুলে রাখা ছিল!
ওই ঘটনার পর থেকে ওয়ার্ডেন রণজিৎ দত্ত আমাদের সঙ্গে আরও মাই ডিয়ার হয়ে গেলেন। একেবারে হৃদমাঝারে রাখব, ছেড়ে দেব না !
যদিও নীচুক্লাসের ছেলেপুলেরা কিঞ্চিৎ হতাশ।
কিন্তু আমাদের কপালটাই খারাপ। এই মধুচন্দ্রিমা বেশি দিন চলেনি। কোনটাই বা চলে!
দুমাসের মাথায় ঘটনাচক্রে সেই রণজিৎদার সঙ্গেই ক্লাস টেন ও ইলেভেনের সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায় দাঁড়িয়ে গেল।
টালা পার্কে বিরাট মেলা। তাতে চিন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের পর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিরাট একজিবিশন। আবার টেলিভিশন রাখা আছে। সেখানে গিয়ে চার আনা দিয়ে আপনিও গান গাইতে পারেন। পুরো পাবলিক আপনাকে পর্দায় গাইতে দেখবে। তবে দিনটা রোববার। ঠিক হল, আগে দুপুর বেলায় আমরা ময়দানে যাব। ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডানের ম্যাচ দেখব। তারপর সেখান থেকে টালা পার্কের প্রদর্শনী দেখে আশ্রমে ফিরব। পুরো প্রোগ্রাম ছকে নিয়ে আমরা সেক্রেটারি মহারাজের সঙ্গে দেখা করলাম।
উনি ও মেজ মহারাজ রাজি। কিন্তু এতগুলো ছেলে, প্রায় পনের জন , তার জন্যে আশ্রমের ডজ ভ্যানটা দেওয়া সম্ভব নয়। সবাইকে বাসে যেতে হবে। আর একজন ক্যাপ্টেন হয়ে আগে ভাগে সবার থেকে ভাড়ার টাকাটা জমা নেবে।
সব হিসেবমত চলছিল।
কিন্তু সেই চোরাগোপ্তা শ্রেণীসংগ্রাম! একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা। ক্লাস এইটের ছেলেগুলো মহারাজকে গিয়ে বলল-- ওরা যাচ্ছে, তো আমরা কি দোষ করলাম? আমাদেরও পারমিশন দিন।
--তোমরা ছোট।
--কীসের ছোট? আমরা দুজন তো প্রদ্যুম্নের সঙ্গেই পড়তাম। আমরা দুজন ক্যাপ্টেন হয়ে আমাদের ক্লাসের ছেলেগুলোকে সামলে সুমলে নিয়ে যাব।
-- এ হয় না। এতগুলো বাচ্চাকে তোমাদের দুজনের ভরসায় ছাড়া যায় না। হ্যাঁ, যদি কোন ওয়ার্ডেন সঙ্গে যেতে রাজি হন, তো ভেবে দেখতে পারি।
ওরা হোমওয়ার্ক করেই এসেছিল।
নরেশ বলল-- ঠিক বলেছেন মহারাজ। আমরা এটা আগেই ভেবেছি। নীচের তলার ওয়ার্ডেন বিনুদা রাজি হয়েছেন। আমরা শুধু পয়সা তুলে ওনার হাতে জমা দেব। উনি দায়িত্ব নিয়ে বলেছেন --কোন অসুবিধে হবে না।
বড় মহারাজ পুরো একমিনিট নরেশের দিকে তাকিয়ে রইলেন , তারপর বললেন--আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমরা যাবে।
কিন্তু মেজমহারাজ সেই ধর্মক্লাসের সময় থেকেই আমাদের উপর চটে ছিলেন। উনি বললেন--একযাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে? ক্লাস টেনের ছেলেরাও ওদের ওয়ার্ডেনকে সঙ্গে নিয়ে যাক, নইলে হবে না।
ক্লাস এইট মহা খুশি।
আমরা বল্লাম-- কুছ পরোয়া নেই। রণজিৎ দত্তকে রাজি করানো কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু কোথায় খচ হচ করছিল-- সিনিয়র ব্যাচের কোন মান-ইজ্জত নেই? ক্লাস এইটের নিয়ম আমাদের জন্যেও?
ভুল বলিনি। উনি রাজি হয়েছেন ---বড় ও মেজমহারাজ দুজনকেই জানিয়ে দিলাম। ব্যস্, হোস্টেলে সাজো সাজো রব। সবাই গড়ের মাঠের ফুটবল দেখার নামে প্রায় নাওয়া খাওয়া ভুলে গেছে। পরিমল দে বলে-- খড়দহ না বালি কোথাকার যেন--একজন নতুন প্লেয়ার খেলবে, তার পায়ের কাজ নাকি দেখার মত।
কেউ কেউ বলল-- ও আমাদের পাড়ার ছেলে, জানিস? ওর পাড়ার নাম জংলা।
যাওয়ার দিন আমরা খেয়ে দেয়ে তৈরি হয়েছি --কিন্তু রণজিৎ দার দেখা নেই। উনি সকাল থেকেই বেপাত্তা, কোথায় গেছেন কেউ জানে না। আমরা জানি উনি ঠিক সময়ে এসে পড়বেন।
ঘড়ির কাঁটা অন্যদিনের থেকে তাড়াতাড়ি ঘুরছে। এইটের ছেলেরা সেজেগুজে ওদের ওয়ার্ডেন বিনুদার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে নরেশ ট্যারা চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ওর সঙ্গীকে বলল-- একটা ইংরেজি প্রোভার্ব শুনেছিস? ম্যান প্রোপোজেস, গড ডিসপোজেস্!
ওর সঙ্গী দোহার ধরল--ধুস্, ওসব পুরনো। আজকের লেটেস্ট শুনে নে। ক্লাস টেন প্রোপোজেস্, রণজিৎ ডিস্পোজেস্! হ্যা-হ্যা হ্যা-হ্যা!
নাঃ, রণজিৎদার কোন পাত্তা নেই। শেষে কি আমরা যারা পুরো প্রোগ্রামটাই বানালাম --আমরাই যেতে পারব না?
আমরা তৈরি হয়ে বড় ও মেজ মহারাজকে ধরলাম।
--আমরা সিনিয়র, ওয়ার্ডেন ছাড়াই যেতে দিন। কোন গন্ডগোল হবেনা।
মেজ মহারাজ গম্ভীর মুখে মাথা নাড়েন। তা হয় না। ওয়ার্ডেন আসলে তবেই, নইলে নয়।
এমন সময় প্রশান্ত দৌড়তে দৌড়তে অফিসে ঢুকল। রণজিৎদা এসে গেছেন। কোন সমস্যাই নেই।
আমরা আবার লাফালাফি করে দোতলায় নিজেদের ঘরে। রণজিৎদা জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় পাজামা পরে লম্বা হয়েছেন।
-- এ কী স্যার ! শিগগির তৈরি হয়ে নিন। একদম সময় নেই। এক্ষুণি বেরোতে হবে।
--কোথায়?
--কোথায় মানে? আগে গড়ের মাঠ, তারপর টালা পার্ক।
--তোমরা যাও।
-- কী বলছেন! আপনি না গেলে অমাদের যেতে দেওয়া হবে না, জানেনই তো!
--আমি টায়র্ড, পারব না ।
--এসব কি বলছেন রণজিৎ দা? সেদিন যে কথা দিলেন?
উনি মুচকি মুচকি হাসছেন।
-- মিন্টু দাশগুপ্তের লেটেস্ট প্যারডি গানটা শুনেছ? সঙ্গম সিনেমার গানের?
'আমার চিঠিখানা পাবার পর, আমাকে তুমি নিজে ভুল বুঝো না।
যে কথা দিয়েছিলেম গো,
সেকথা আমি ফিরিয়ে নিলেম গো।'
তোমরা অন্য কোন ওয়ার্ডেনকে বল।
-- রণজিৎদা! স্যার! প্লীজ, এখন সময় নেই। উঠুন, জামাপ্যান্ট পরে নিন।
--বললাম তো! অনেকগুলো ক্লাস ছিল। ভীষণ টায়ার্ড। অন্য কাউকে--
গুরু অমিয়দা খিঁচিয়ে ওঠে।
--আগে বলেন নি কেন? এখন বলছেন? শেষ সময়ে কাকে বলব? ইয়ার্কি মারার আর--
ছিটকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন রোগা তালঢ্যাঙা রণজিৎদা--যেন নোয়ানো বাঁশের ঝাড়ের একটা কঞ্চি ।
--বেরিয়ে যাও! অল অফ ইউ! জাস্ট গেট আউট!